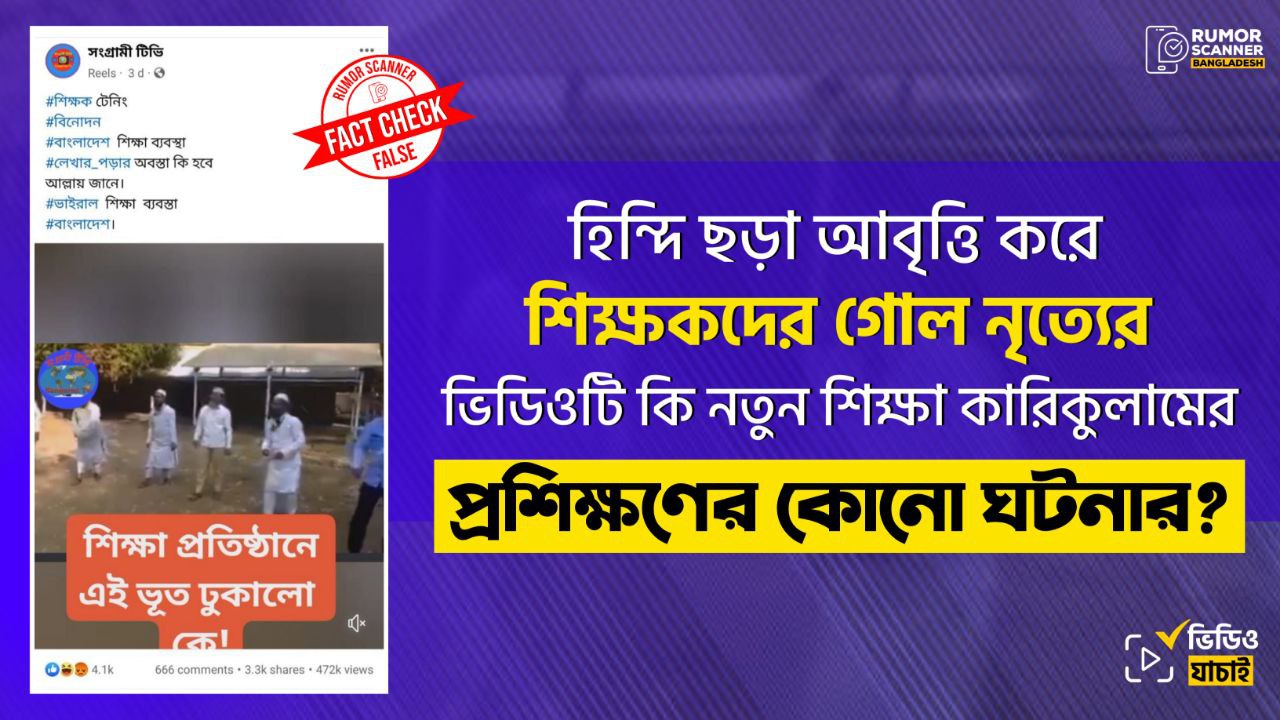সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনে অনুদান পাঠানো, ফিলিস্তিনের প্রতি সরাসরি সমর্থন ও তাদের সমর্থনে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি প্রবর্তন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ আলোচিত আকিজ গ্রুপ ও তাদের কোলা ব্র্যান্ড মোজো।
অপরদিকে একই সময়ে একই ইস্যুর কারণে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে মার্কিন কোম্পানির পণ্য কোকাকোলা তথা কোককে ইসরায়েলকে সমর্থণকারী কোম্পানির পণ্য হিসেবে বর্জন করা হচ্ছে। কোকাকোলা বয়কটের ফলে স্থানীয় সোডা পণ্যের বিক্রি বেড়েছে এসব দেশে। এই যেমন কোকা কোলা বয়কটের ফলে বিদেশি ব্র্যান্ডের সাথে প্রতিযোগিতায় ধুকতে থাকা মিশরের স্থানীয় সোডা প্রস্তুতকারক স্পিরো স্প্যাথিস এর বিক্রি বেড়েছে প্রায় ৩০০ শতাংশ।
ফিলিস্তিন ইস্যুতে মোজোর আলোচিত হওয়া এবং কোকের বয়কটের ফলশ্রুতিতে সামাজিক মাধ্যমে মোজো বনাম কোক শীর্ষক একটি আলোচনার জন্ম নেয়। এ সময় কেউ কেউ কোক স্টুডিও বাংলার মতো মোজো স্টুডিও বাংলা চাই এমন কিছু পোস্ট করে। এরপরই ফেসবুকে নিজেদের মোজোর অফিশিয়াল উদ্যোগ হিসেবে উপস্থাপন করে উদয় ঘটে মোজো স্টুডিও বাংলা নামের একটি ফেসবুক পেজের।
মোজো স্টুডিও বাংলা ফেসবুক পেজ
Mojo Studio Bangla নামের ফেসবুক পেজটি গত ২ ডিসেম্বর তৈরি করা হয়। পেজটির পক্ষ থেকে এটিকে মোজোর অফিশিয়াল পেজ হিসেবে উপস্থাপন করে কোক স্টুডিও বাংলার বিপরীতে মোজো স্টুডিও বাংলা’র ঘোষণা দেওয়া হয়। লোকজনও এটিকে মোজোর আসল পেজ ধরে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং পেজটি প্রচার করে।

মোজোর অফিশিয়াল উদ্যোগ বোঝাতে সময় টিভির ফটোকার্ড এডিট করে প্রচার
গত ৪ ডিসেম্বর সোমবার পেজটিতে সময় টেলিভিশনের ফটোকার্ডে “কবে শুরু হতে যাচ্ছে মোজো স্টুডিও বাংলা” শিরোনামের একটি সংবাদ পোস্ট করা হয়। তবে অনুসন্ধানে সময় টিভির ফেসবুক পেজে এমন কোনো সংবাদের ফটোকার্ড প্রকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মূলত মোজো স্টুডিও বাংলা উদ্যোগটি আসল এটি বোঝানো এবং বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য পেজটি সময় টিভির ফটোকার্ড এডিট করে ভুয়া এ সংবাদ প্রচার করে।
লক্ষাধিক টাকার গিভওয়ে ঘোষণা
Mojo Studio Bangla পেজটি তৈরির দু-তিন দিনের মধ্যে প্রায় ৬ হাজার ফলোয়ার লাভ করে এবং পরবর্তীতে আরও বেশি ফলোয়ার পেতে নিজেদের মোজোর অফিশিয়াল হিসেবে উপস্থাপন করে পেজটি থেকে আইফোন প্রো ম্যাক্সসহ লাখ টাকার গিফট দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রমোশনাল গিভওয়ে পোস্ট করা হয়। শর্ত হিসেবে পেজে লাইক দেওয়া, গিভওয়ে পোস্টটি শেয়ার করা এবং Mojo Studio Bangla নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে বলা হয়। গিভওয়ে ঘোষণার পর লোকজন সেটিকে মোজোর উদ্যোগ ভেবে অংশগ্রহণ করে। যার ফলে তাদের ইউটিউবে সাবস্ক্রাইবারও বাড়তে থাকে। এখন পর্যন্ত সেই ইউটিউব চ্যানেলে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি সাবস্ক্রাইবার রয়েছে।

মোজো স্টুডিও বাংলা চাই নামের একটি ইভেন্ট এর সাথে মোজো স্টুডিও বাংলা পেজের যোগসূত্র
অনুসন্ধানে কোক স্টুডিওর পরিবর্তে মোজো স্টুডিও বাংলা চাই নামের একটি ইভেন্ট খুঁজে পাওয়া যায়। গত ২৭ নভেম্বর Faiyaz Ef Ti নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ইভেন্টটি তৈরি করা হয়। ঐ একই অ্যাকাউন্ট থেকে “MOJO STUDIO VS COKE STUDIO এর মারামারি চাই” নামের অপর একটি ইভেন্টও তৈরি করা হয়।

পরবর্তীতে ২ ডিসেম্বর তৈরি হওয়া কোক স্টুডিও বাংলা নামের পেজটির একাধিক পোস্টে Faiyaz Ef Ti নামের অ্যাকাউন্টটিকে ট্যাগ করতে দেখা যায়। যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় ২৭ নভেম্বর ‘কোক স্টুডিওর পরিবর্তে মোজো স্টুডিও বাংলা চাই’ শীর্ষক ইভেন্ট তৈরি করা আইডিটিই Mojo Studio Bangla নামের পেজটির পিছনে রয়েছে।

মোজো স্টুডিও বাংলা মোজোর কোনো অফিশিয়াল পেজ নয়
মোজো স্টুডিও বাংলা পেজটি মোজোর অফিশিয়াল উদ্যোগ ধরে নিয়ে যখন রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ছিল। ঠিক তখন বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানে নামে রিউমর স্ক্যানার। রিউমর স্ক্যানার টিমের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় মোজোর সাথে। পেজটির বিষয়ে জানতে চাইলে মোজো কর্তৃপক্ষ জানায়, “মোজো স্টুডিও বাংলা মোজোর অফিশিয়াল কোনো পেজ না। অন্য কেউ একজন এই নামে পেজ চালাচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে পেজটি রিমুভ করার চেষ্টা চালাচ্ছি।”
পরবর্তীতে মোজোর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকেও একটি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ঐ পেজটিকে ভুয়া নিশ্চিত করা হয়। পোস্টটিতে লেখা হয়, “সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, Mojo Studio Bangla নামে একটি ফেইসবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করা হয়েছে যা Mojo কর্তৃক কোন অফিশিয়াল পেইজ নয়, এটি একটি Fake পেইজ যা দ্বারা মানুষকে প্রলোভন এবং বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। মোজো কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তাই সকলকে বিভ্রান্ত না হয়ে Mojo ভেরিফাইড পেইজের সাথে থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।”

সুতরাং, মোজো স্টুডিও বাংলা নামের পেজটি মোজোর অফিশিয়াল কোনো পেজ নয়, প্রকৃতপক্ষে মোজোর অফিশিয়াল উদ্যোগ দাবি করা এ পেজটি ছিল একটি ভুয়া পেজ।
তথ্যসূত্র
- Rumor Scanner’s analysis
- Statement from Mojo