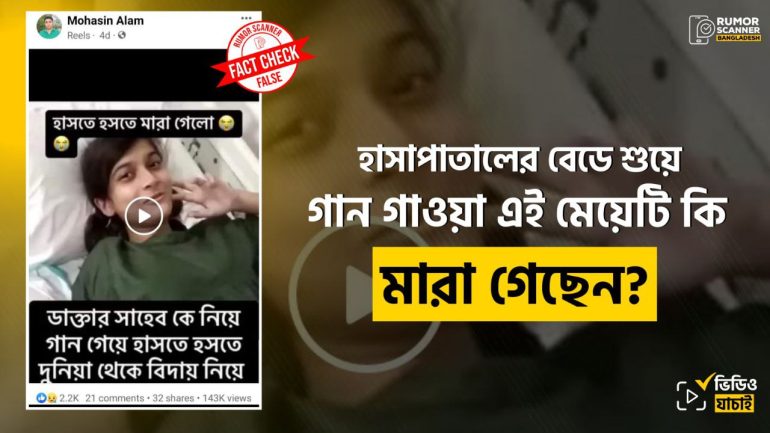গত ১৯ নভেম্বর ভারতে আয়োজিত আইসিসি ওডিআই ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া। এই জয়ের পর নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দলটির সদস্য মিচেল মার্শের একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে, যাতে দেখা যায় তিনি বিশ্বকাপ ট্রফির উপর পা তুলে বসে আছেন। পরবর্তীতে এই উদযাপনকে ভারতীয়দের জন্য অসম্মানজনক জানিয়ে ভারতের উত্তর প্রদেশের নাগরিক পণ্ডিত কেশব মিচেল মার্শের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন দাবিতে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। কতিপয় গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, পণ্ডিত কেশব মিচেল মার্শের বিরুদ্ধে থানায় মামলাই দায়ের করেছেন।

উক্ত দাবিগুলোতে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন দেখুন ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, ইত্তেফাক, ঢাকা টাইমস, কালবেলা, ঢাকা পোস্ট, চ্যানেল আই, বাংলা ট্রিবিউন, কালের কণ্ঠ, চ্যানেল২৪, আমাদের সময়, যায়যায়দিন, প্রতিদিনের বাংলাদেশ, বাংলাভিশন (ফেসবুক), অনফিল্ড (ফেসবুক), অলরাউন্ডার (ফেসবুক), দেশটিভি, ডেইলি ক্রিকেট (ফেসবুক), বাংলানিউজ২৪, ঢাকা মেইল, আজকের দর্পণ, আমার বার্তা, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ক্রিকফ্রেন্জি, বিডিক্রিকটাইম, সংবাদ প্রকাশ, ডেইলি বাংলাদেশ, একুশে সংবাদ, রাইজিং বিডি, সোনালী নিউজ, বাংলা২৪লাইভ নিউজপেপার, জুমবাংলা, ডেল্টা টাইমস, এমটিনিউজ২৪, তরঙ্গ নিউজ।

একই দাবিতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন দেখুন স্পোর্টস কিডা, ওপিইন্ডিয়া, ইটিভি ভারত।

একই দাবিতে গণমাধ্যমের ফেসবুক পেজসহ অন্যান্য ব্যবহারকারীদের পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ)।
একই দাবিতে গণমাধ্যমের ইউটিউব চ্যানেলসহ অন্যান্য ব্যবহারকারীদের ভিডিও দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ)।
ফ্যাক্টচেক
রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, ভারতে মিচেল মার্শের বিরুদ্ধে মামলা বা এফআইআর দায়েরের দাবিটি সঠিক নয় বরং এক ব্যক্তির করা অভিযোগকে উক্ত দাবিতে প্রচার করা হলেও পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগ আমলে নেয়া হয়নি।
এ বিষয়ে অনুসন্ধানের শুরুতে এক্সে (সাবেক টুইটার) ভারতের সংবাদমাধ্যম The Quint এর সাংবাদিক পিয়ুস রায়ের একটি টুইট নজরে আসে আমাদের। গত ২৪ নভেম্বরের উক্ত টুইটে পিয়ুস বলছিলেন, Bhrashtachar Virodhi Sena নামে একটি সংগঠনের জাতীয় প্রেসিডেন্ট পন্ডিত কেশব দেব মিচেল মার্শের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে একটি অভিযোগ পাঠিয়েছেন আলীগড়ের দিল্লী গেট পুলিশ স্টেশনে। পিয়ুস অভিযোগপত্রটির একটি ছবিও যুক্ত করেছেন টুইটে।

আমরা এ বিষয়ে জানতে পন্ডিত কেশব দেবের সাথে কথা বলেছি। কেশব রিউমর স্ক্যানারকে বলেছেন, তিনি গত ২১ নভেম্বর এই অভিযোগটি থানায় পৌঁছে দেন৷ সেদিনের একটি ছবিও তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। কেশব আমাদের কাছে স্থানীয় একটি পত্রিকার ক্লিপ পাঠিয়ে উক্ত সংবাদের বরাতে জানান, তার অভিযোগটির বিষয়ে ইন্সপেক্টর নরেন্দ্র শর্মা জানিয়েছেন, সাইবার সেলের মাধ্যমে এ বিষয়ে তদন্ত করা হবে।

জনাব কেশব বলছেন, তিনি অভিযোগটির একটি কপি ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছেও পাঠিয়েছেন।
ক্রীড়ামন্ত্রীকে পাঠানো অভিযোগটির কপি তিনি রিউমর স্ক্যানার টিমকেও দিয়েছেন৷

তবে আলীগড় পুলিশ বলছে, তারা এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ আমলে নেয়নি৷ আলীগড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ম্রিগাঙ্ক শেখর পাঠক এক্সে এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে জানিয়েছেন, মার্শের বিরুদ্ধে আলিগড়ের কোনো থানাতেই কোনো অভিযোগ, মামলা বা এফআইআর আমলে নেয়া হয়নি।
ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ফ্যাক্টচেকার অঙ্কিতা দেশকারের কাছে এফআইআর এবং অভিযোগকে ভারতে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় সে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম আমরা। তিনি রিউমর স্ক্যানারকে বলেছেন, এফআইআর তখনই করা যায় যখন অভিযোগকারী তার অভিযোগের বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত থাকেন। এর ফলে তিনি বিষয়টি নিয়ে তদন্তের আর্জি জানাতে পারেন। অভিযোগ যে কেউই জানাতে পারে এবং সেটা কেউ তুলেও নিতে পারে। তবে এফআইআর করা হলে তা আপনি তুলে নিতে পারবেন না।
মূলত, সম্প্রতি ভারতে আইসিসি ওডিআই ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার দলের মিচেল মার্শের একটি ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে দেখা যায় তিনি বিশ্বকাপ ট্রফির উপর পা তুলে বসে আছেন। পরবর্তীতে এই উদযাপনকে ভারতীয়দের জন্য অসম্মানজনক জানিয়ে ভারতের পণ্ডিত কেশব নামে এক ব্যক্তি মিচেল মার্শের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর (কতিপয় গণমাধ্যমে মামলা দাবি) দায়ের করেছেন দাবিতে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, এফআইআর বা মামলা নয়, পণ্ডিত কেশব এ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দিয়েছেন থানায়৷ তবে সেই অভিযোগ আমলে নেয়নি সংশ্লিষ্ট থানা। আলীগড় পুলিশ বলছে, মার্শের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা এফআইআর হয়নি।
সুতরাং, বিশ্বকাপের ট্রফি পায়ের নিচে রাখাকে ভারতীয়দের জন্য অসম্মানজনক জানিয়ে ভারতের এক ব্যক্তির মিচেল মার্শের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করার ঘটনাকে মার্শের বিরুদ্ধে মামলা বা এফআইআর দায়ের করা হয়েছে দাবিতে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে; যা বিভ্রান্তিকর।