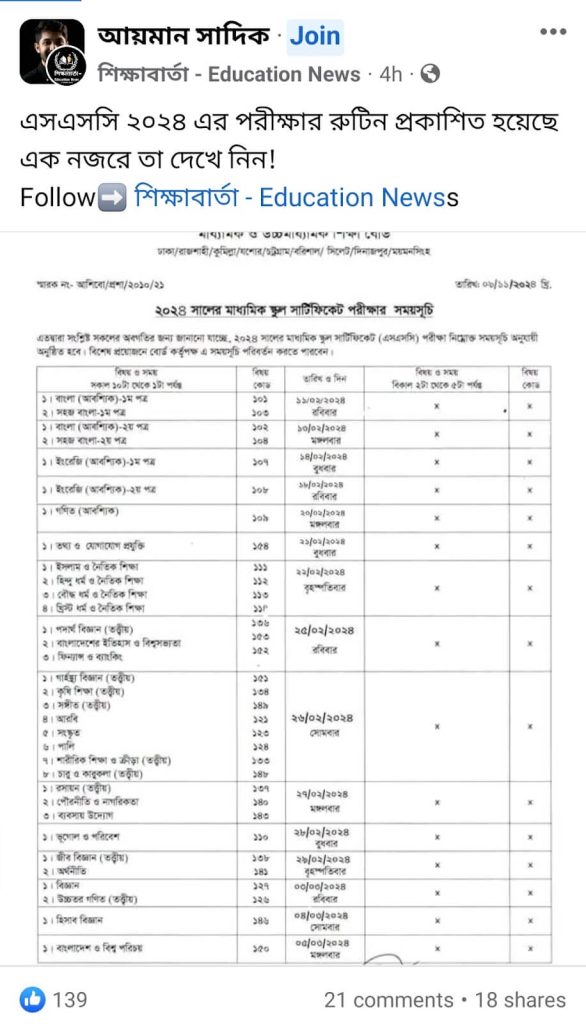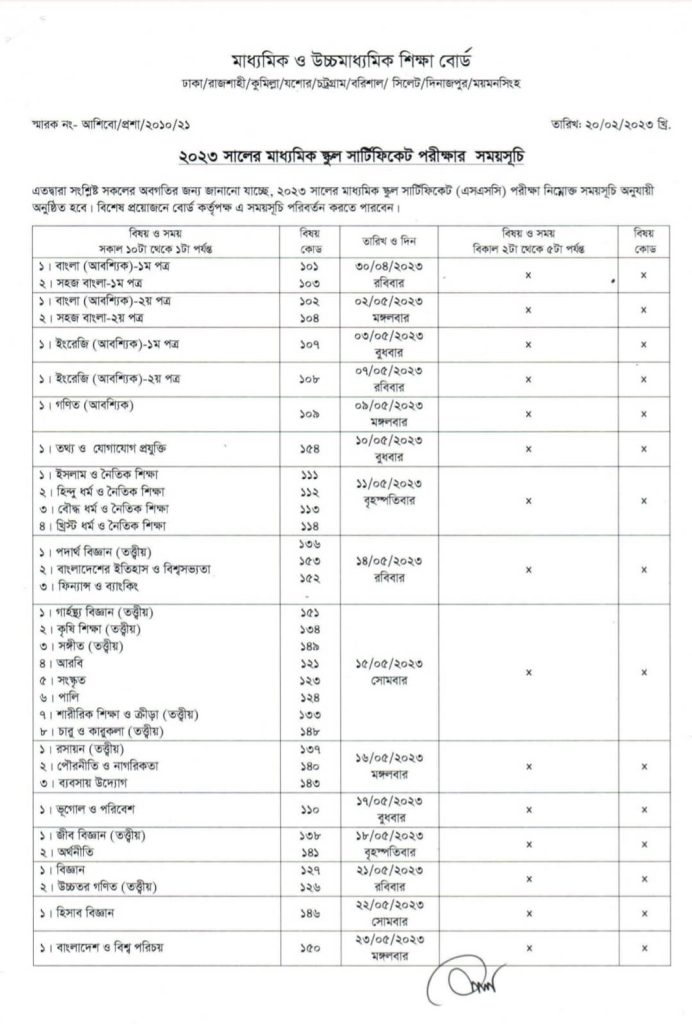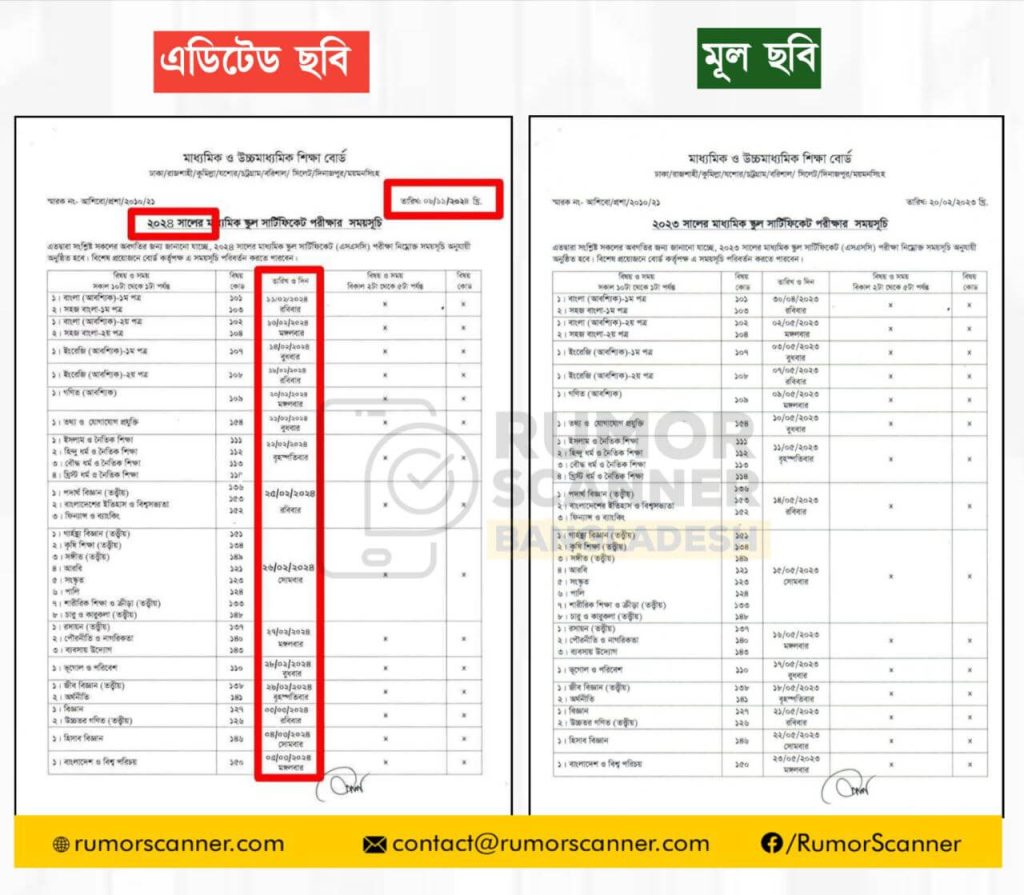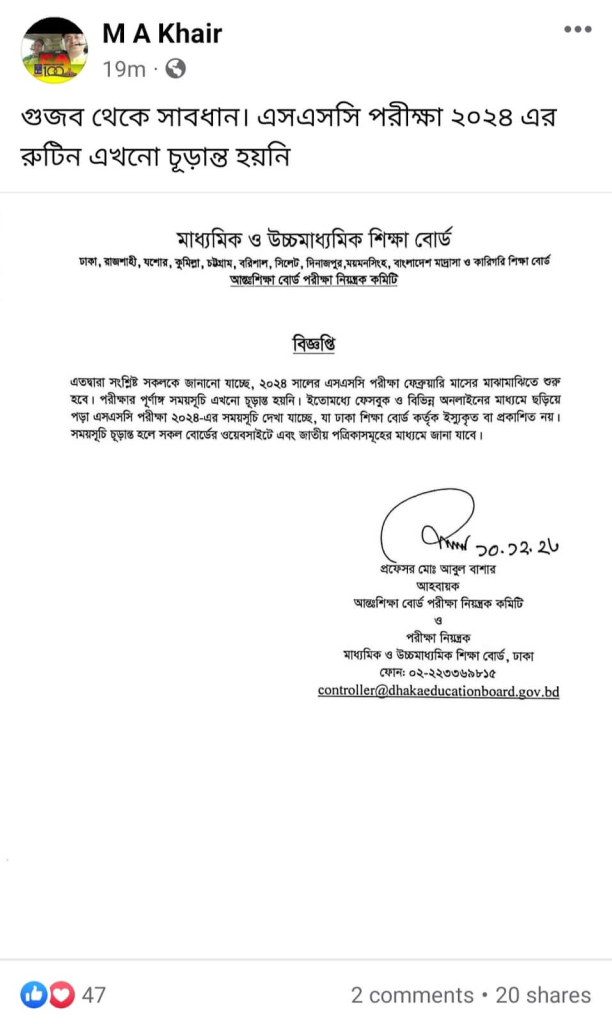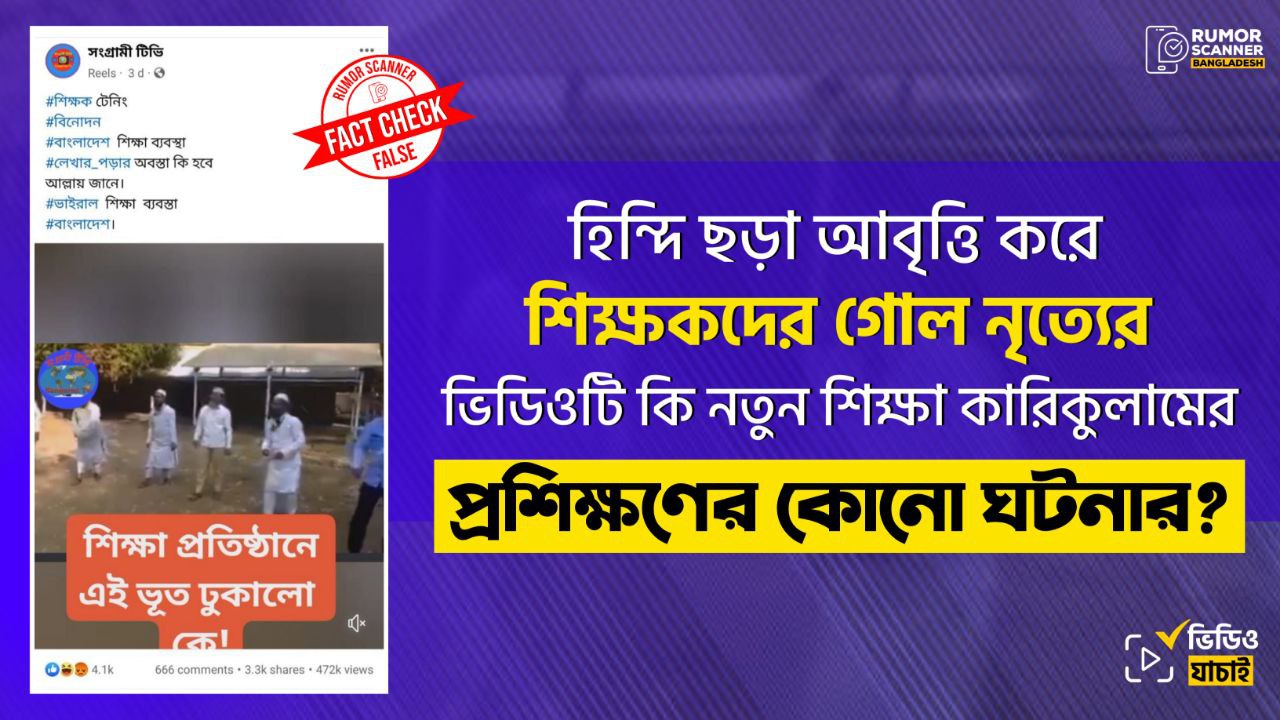সম্প্রতি, ফিলিস্তিন নয় যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি রাখতে ইসরাইলকে সাপোর্ট করছে বিএনপি– শীর্ষক ক্যাপশনে তারেক রহমানের বক্তব্য দাবিতে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।
৪৯ সেকেন্ডের ভিডিওটিতে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বলতে শোনা যায়, প্রিয় দেশবাসী! আসসালামু আলাইকুম। আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় অনেকেই জানতে চাচ্ছেন, ইসরায়েল- হামাস ইস্যুতে বিএনপি’র অবস্থান কী? বলে রাখা ভালো বাংলাদেশের রাজনীতি খুবই জটিল। ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ। তারা সাপোর্ট করছে ফিলিস্তিনকে। এখন যদি আমরা ফিলিস্তিনকে সাপোর্ট করি তাহলে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের উপর বেজার হবে, নষ্ট হবে আমাদের সুসম্পর্ক। তাই চুপচাপ থাকবো। সুযোগ বুঝে সিদ্ধান্ত নেব। কাকে সাপোর্ট করলে ফায়দা আমাদের। সবাইকে ধন্যবাদ! বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ।

ফেসবুকে প্রচারিত এমন কিছু পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।
ফ্যাক্টচেক
রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুলন্ধানে দেখা যায়, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি রাখতে ইসরায়েলকে সাপোর্ট করছে বিএনপি শীর্ষক কোনো মন্তব্য করেননি নয় বরং তারেক রহমানের ভিন্ন ঘটনার বক্তব্যের ভিডিওর স্ক্রিনশট নিয়ে তাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্যে আলোচিত দাবি সম্বলিত অডিও যুক্ত করে উক্ত ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে।
শুরুতে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এমন কোনো বক্তব্য দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে রিউমর স্ক্যানার টিম। অনুসন্ধানে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড সার্চ করে মূলধারার গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের কোনো বিশ্বস্ত সূত্র হতে উক্ত বক্তব্য সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
এছাড়া, তারেক রহমান দেশবাসী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যের ভিডিও তাঁর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়ে থাকে।
তবে, আলোচিত ভিডিওটির বিষয়ে অনুসন্ধানে তারেক রহমানের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ পর্যবেক্ষণ করে এ সংক্রান্ত কোনো পোস্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি।
পাশাপাশি, বিএনপি’র মিডিয়া সেল এবং বিএনপি’র অফিসিয়াল ফেসবুক পেজেও উক্ত ভিডিও সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
পরবর্তীতে বক্তব্যটির বিষয়ে অনুসন্ধানে রিভার্স ইমেজ সার্চ করলে তারেক রহমানের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গত ২৫ জুলাই “লন্ডন হতে সরাসরি। ২৫ জুলাই ২০২৩, মঙ্গলবার ২৭ জুলাই ঢাকার মহাসমাবেশ সফল করার আহবান জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য”- শীর্ষক ক্যাপশনে প্রকাশিত একটি ভিডিওর সাথে আলোচিত ভিডিওটির পোশাক এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের মিল খুঁজে (আর্কাইভ) পাওয়া যায়। তবে, এই ভিডিওতে তারেক রহমান ইসরায়েল-ফিলিস্তিন নিয়ে আলোচিত ভিডিওটিতে থাকা বক্তব্যটি দেননি।

এতে প্রতীয়মান হয় যে গত ২৫ জুলাই তারেক রহমানের দেওয়া ভিডিও বক্তব্যটির কোনো একটি অংশ থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে আলোচিত ভিডিওটিতে ব্যবহার করা হয়েছে।
আলোচিত ভিডিওতে থাকা অসংগতি
৪৯ সেকেন্ডের আলোচিত ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ভিডিওতে থাকা কণ্ঠের সাথে তারেক রহমানের কণ্ঠের মিল নেই এবং কথা বলার সময়ও কণ্ঠস্বরের কোনো পরিবর্তন নেই।
এছাড়া, চোখের নড়াচড়া ও কথা বলার সময় ঠোঁটর নড়াচড়ার মধ্যেও অসংগতি রয়েছে।
মূলত, গত ২৭ জুলাই বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশবাসী ও নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে ঢাকার মহাসমাবেশ সফল করার আহবান জানিয়ে একটি বক্তব্য দেন। সেই বক্তব্য তাঁর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়। পরবর্তীতে সেই ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় সম্পাদনার মাধ্যমে তাতে ফিলিস্তিন নয় যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি রাখতে ইসরাইলকে সাপোর্ট করছে বিএনপি শীর্ষক অডিও যুক্ত করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত ০৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে ‘অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড’ নামে হামলা শুরু করে। এই হামলার প্রেক্ষিতে ইসরায়েলও হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকায় পাল্টা হামলা চালায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা উক্ত ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান নিয়ে বক্তব্য দেয় এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।
সুতরাং, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের ঘটনায় বিএনপি’র অবস্থান নিয়ে তারেক রহমানের বক্তব্যের দৃশ্য দাবিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রচার করা হচ্ছে; যা বিকৃত বা এডিটেড।
তথ্যসূত্র
- Tarique Rahman Facebook Page
- BNP Official Facebook Page
- BNP Media Cell
- Tarique Rahman Facebook Post
- Rumor Scanner’s Own Analysis