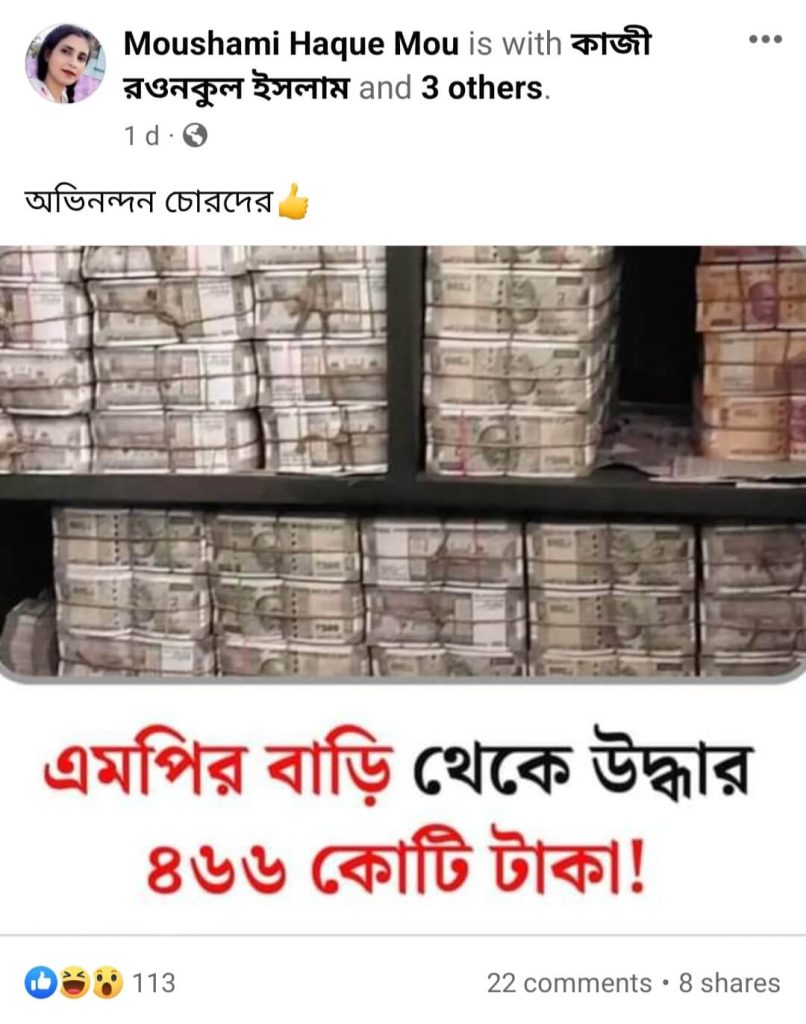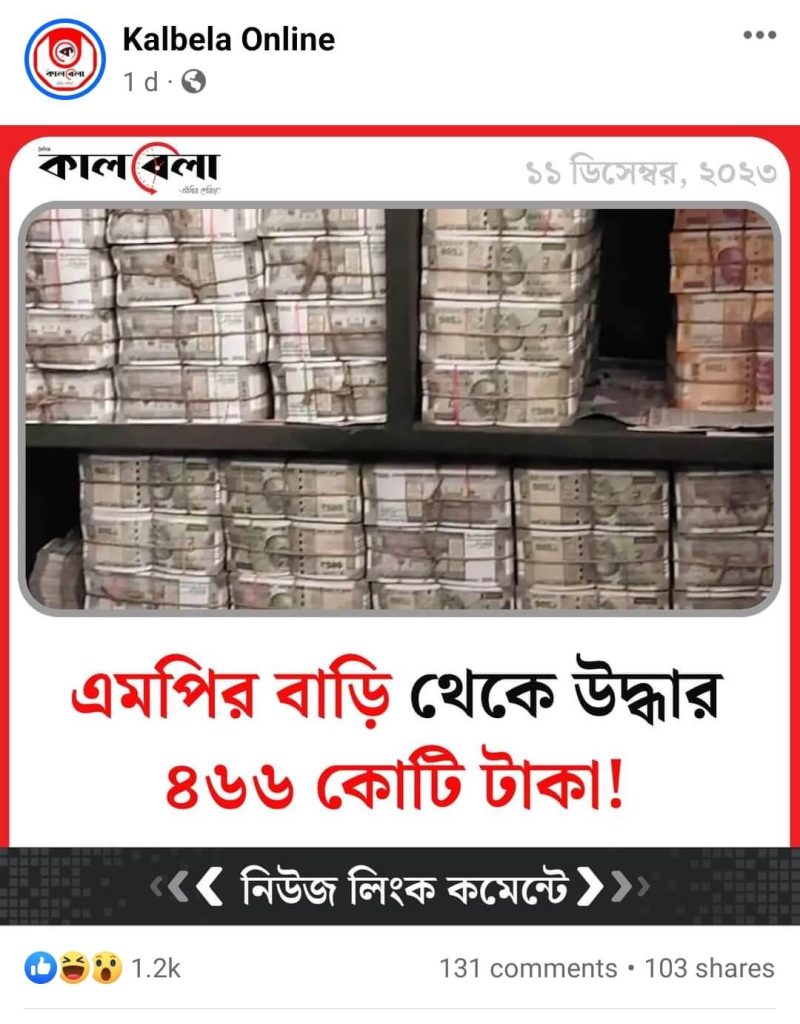সম্প্রতি, ‘আর বাঁচানো গেল না খালেদা জিয়াকে’ শীর্ষক শিরোনামে একটি ভিডিও ইন্টারনেটে প্রচার করা হয়েছে।

উক্ত দাবিতে ফেসবুকে প্রচারিত কিছু ভিডিও দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

একই দাবিতে টিকটকে প্রচারিত কিছু ভিডিও দেখুন এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।
ফ্যাক্টচেক
রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মারা যাওয়ার খবরটি সঠিক নয় বরং ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ভিডিওর সাথে আলোচিত দাবি সম্বলিত অডিও যুক্ত করে উক্ত ভিডিওটি প্রচার করা হয়েছে।
অনুসন্ধানের শুরুতে আলোচিত দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটি পর্যালোচনা করে রিউমর স্ক্যানার টিম। এতে দেখা যায়, ভিডিওটির শুরুতে যমুনা টেলিভিশনের উপস্থাপিকাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মারা গেছেন।
এরপরই সময় টিভির একটি ফুটেজ দেখানো হয় যেখানে রুহুল কবির রিজভীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তীতে একজন ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, আমাদের হাতে আর কোনো চিকিৎসা নেই এই মুহুর্তে এবং সর্বপরি, একজন ব্যক্তিকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে দেখা যায়।
এই ভিডিওটির নিচে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে খালেদা জিয়া, হাসিনা খালেদা জিয়াকে হত্যা করতে চায় শীর্ষক একটি লেখা দেখতে পাওয়া যায়।
এরপরই ভিডিওটির উপস্থাপক ক্যামেরার সামনে আসেন এবং তিনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন, মৃত্যু সজ্জায় খালেদা জিয়া। যেকোনো সময় মারা যাবে। সিসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। বিএনপির ভেতরে এই মুহুর্তে শোকের ছায়া।
এরপর তিনি খালেদা জিয়ার বর্তমান অবস্থা জানতে দর্শকদের পুরো ভিডিওটি দেখতে বলেন। তবে ভিডিওটির কোথাও খালেদা জিয়া মারা গেছেন শীর্ষক তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।
ভিডিও যাচাই ১
আলোচিত ভিডিওটির শুরুতে দেখানো যমুনা টিভির ফুটেজটি অনুসন্ধানে ভিডিওতে দেখানো ‘অবরোধ সমর্থনে বিএনপির মিছিল’ শীর্ষক লেখাটির সূত্র ধরে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে যমুনা টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলে গত ১২ ডিসেম্বর অবরোধের সমর্থনে রাজধানীতে বিএনপির মশাল মিছিল | BNP blockade | Jamuna TV শীর্ষক শিরোনামে প্রচারিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

ভিডিওটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আলোচিত ভিডিওর শুরুতে দেখানো যমুনা টিভির উপস্থাপিকার ফুটেজের সাথে উক্ত ভিডিওটির মিল রয়েছে।

তবে উক্ত ভিডিওটিতে উপস্থাপিকাকে বলতে শোনা যায়, ‘সরকার পতনের দাবিতে টানা ৩৬ ঘন্টা অবরোধ পালন করছে বিএনপি। কর্মসূচির সমর্থনে রাতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মশাল মিছিল করে দলীয় নেতাকর্মীরা। দলটির অভিযোগ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে বের হওয়া মশাল মিছিলে পুলিশ হামলা চালিয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কয়েকটি এলাকায় বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।’ যার সাথে আলোচিত ভিডিওটির কোনো মিল নেই।
অর্থাৎ, ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় উক্ত ভিডিওতে ভিন্ন অডিও যুক্ত করে প্রচার করা হয়েছে।
ভিডিও যাচাই ২
পরবর্তী ভিডিওটিতে ‘সময় টিভি’র একটি ফুটেজ দেখানো হয়, যেখানে বিএনপির সিনিয়র সুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে দেখতে পাওয়া যায়। ভিডিওটির নিচের দিকে, ‘শর্তসাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য বেগম জিয়ার সাজা স্থগিত’ শীর্ষক লেখাটি দেখতে পাওয়া যায়। যার সূত্র ধরে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে সময় টিভির প্রতিবেদনটি পাওয়া না গেলেও যমুনা টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলে ২০২০ সালের ২৪ মার্চ খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত শুনেই হাসপাতালে রিজভী | Jamuna TV শীর্ষক শিরোনামে প্রচারিত একটি ভিডিও প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়।

ভিডিওটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আলোচিত ভিডিওর রুহুল কবির রিজভীর সাথে উক্ত ভিডিওর রিজভীর শার্টের রঙ এবং চেকের সাথে হুবহু মিল রয়েছে।

এছাড়াও, দুই ভিডিওতেই তার মুখে মাস্ক দেখতে পাওয়া যায়। আর আলোচিত ভিডিওটির উপরে দেখতে পাওয়া যায় ভিডিওটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে এবং কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে পাওয়া যমুনা টিভির প্রতিবেদনের শিরোনাম থেকেও জানা যায়, উক্ত ভিডিওটি হাসপাতালে ধারণ করা হয়েছে।
ভিডিও যাচাই ৩
আলোচিত ভিডিওটিতে এরপর একজন ব্যক্তিকে মাইক্রোফোন হাতে কথা বলতে দেখা যায়। উক্ত ভিডিওর ডান পাশে উপরে ‘NewsNow বাংলা’ নামের একটি লোগো দেখা যায়। লোগোটির সূত্র ধরে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে NEWS NOW বাংলা-এর ফেসবুক পেজে গত ৯ অক্টোবর আমাদের হাতে আর কোনো চিকিৎসা নানাই, খালেদা জিয়া বেশি দিন বাঁচবে না: বোর্ড চিকিৎসক শীর্ষক শিরোনামে প্রচারিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

ভিডিওটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উক্ত ভিডিওটি মূলত খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্যে গঠন করা বোর্ডের বোর্ড চিকিৎসকের। তিনি মূলত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার অবস্থা বর্ণনা করছিলেন। যেখানে তিনি সাংবাদিকদের জানান তার উন্নত চিকিৎসার জন্যে তাকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া উত্তম।
ভিডিও যাচাই ৪
আলোচিত ভিডিওটিতে উপস্থাপক দর্শকদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ যে ভিডিওটি দেখান তার সূত্র অনুসন্ধানে ভিডিওটির কয়েকটি কি-ফ্রেম নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে Dr. Fayzul Huq Voice নামের একটি ফেসবুক পেজে গত ৯ অক্টোবর জীবন নিয়ে লড়ছেন বেগম জিয়া। চিকিৎসকরা খালেদা জিয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। ডঃ ফয়জুল হক। শীর্ষক শিরোনামে প্রচারিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

ভিডিওটি মূলত ৯ অক্টোবর খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য বিষয়ে বোর্ড চিকিৎসকদের সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বিবৃতির পর প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত ভিডিওতে খালেদা জিয়ার মারা যাওয়ার বিষয়ে কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।
এছাড়াও বিভিন্ন কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে কোনো গণমাধ্যমে-ই খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ খুঁজে পাওযা যায়নি।
মূলত, বিগত চার মাসের বেশি সময় ধরে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া। গত ১১ ডিসেম্বর তার কিছু শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে তাকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ)-তে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা প্রদানের পর পুনরায় কেবিনে স্থানান্তর করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি, ‘আর বাঁচানো গেল না খালেদা জিয়াকে’ শীর্ষক শিরোনামে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। তবে রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে দেখা যায়, আলোচিত ভিডিওটি মূলত যমুনা টিভি ও সময় টিভির ভিন্ন ঘটনার দুটি পুরোনো ফুটেজে ভিন্ন ভিন্ন অডিও যুক্ত করে তার সাথে আরেকটি সংবাদের এবং ইন্টারনেটে প্রচারিত ভিন্ন ঘটনার ভিডিও যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে খালেদা জিয়ার মৃত্যু বিষয়ক কোনো তথ্য নেই।
সুতরাং, আর বাঁচানো গেল না খালেদা জিয়াকে শীর্ষক দাবিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত তথ্যটি মিথ্যা।
তথ্যসূত্র
- Jamuna TV Youtube Channel: (3) অবরোধের সমর্থনে রাজধানীতে বিএনপির মশাল মিছিল | BNP blockade | Jamuna TV – YouTube
- Jamuna TV Youtube Channel: (3) খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত শুনেই হাসপাতালে রিজভী | Jamuna TV – YouTube
- News Now বাংলা Facebook Page: Video
- Dr. Fayzul Huq Voice Facebook Page: Video