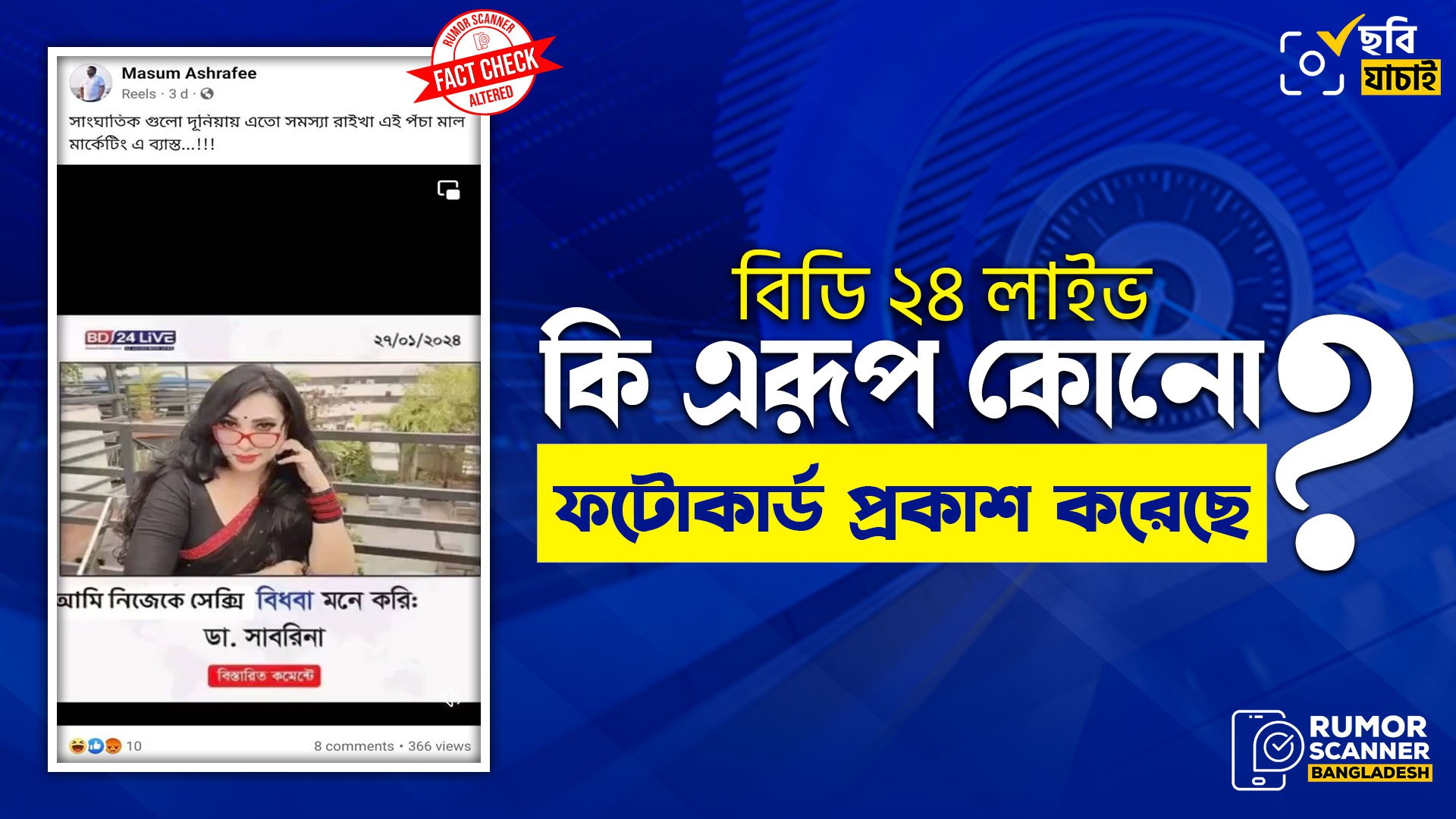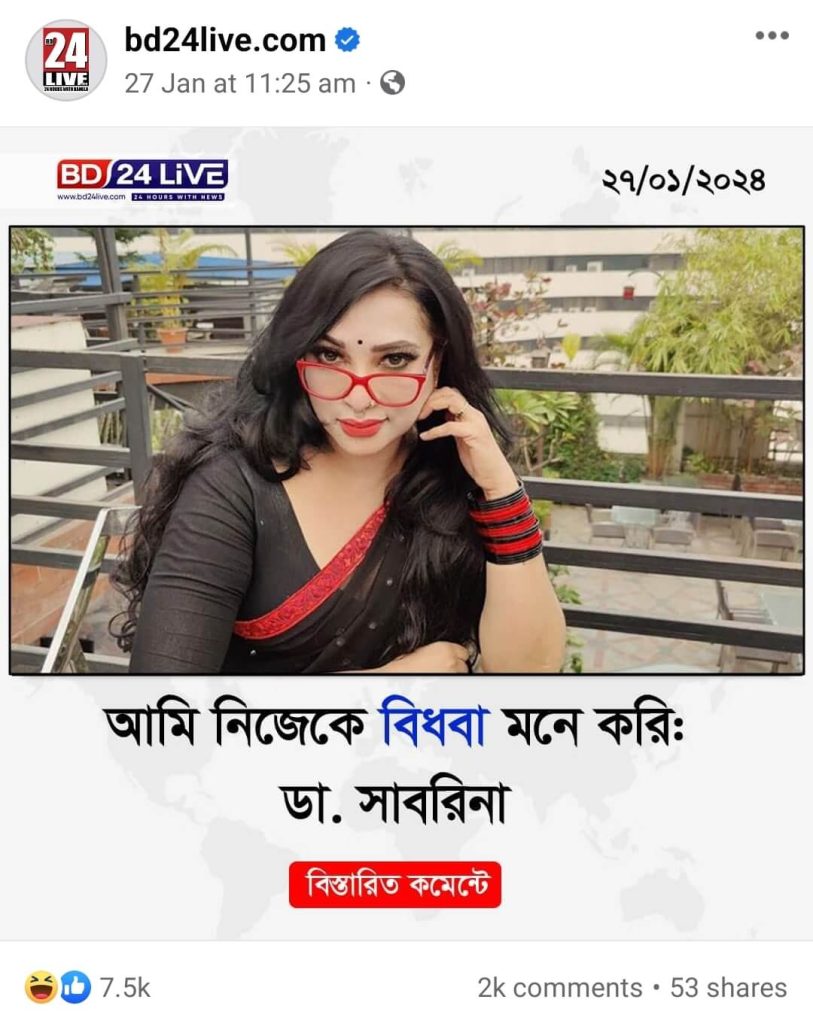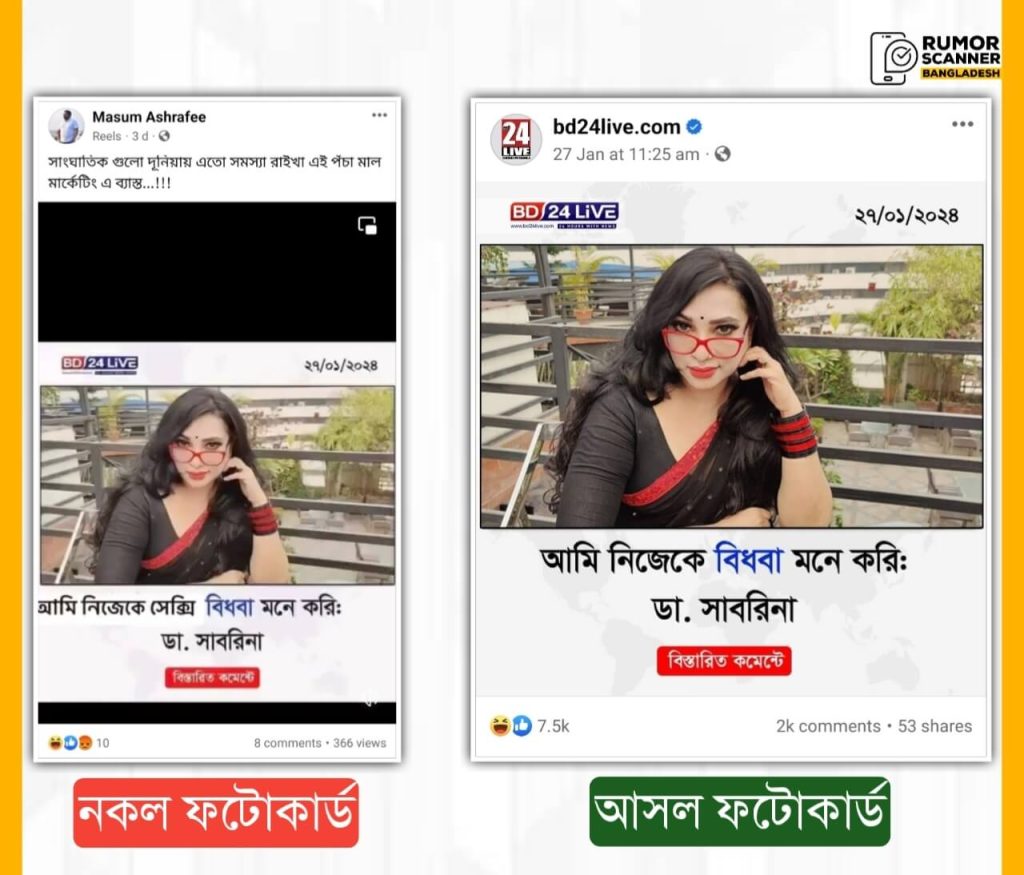সম্প্রতি, মাধ্যমিক পর্যায়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ৫ হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হবে দাবিতে ‘৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি: প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের ৫ হাজার টাকা সহায়তা আবেদন শুরু’ শীর্ষক একটি তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

ফেসবুকে প্রচারিত এমন কিছু পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।
ফ্যাক্টচেক
রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে দেখা যায়, মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ৫ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করার তথ্যটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণিতে) ২০২৪ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত/ অধ্যয়নরত শুধুমাত্র অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ৫ হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হবে।
অনুসন্ধানের শুরুতে আলোচিত দাবিতে প্রচারিত পোস্টগুলো পর্যবেক্ষণ করে রিউমর স্ক্যানার। এতে দেখা যায়, বেশ কয়েকটি পোস্টে তথ্যসূত্র হিসেবে ‘শিক্ষাবার্তা’ তথ্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

উক্ত তথ্যের সূত্র ধরে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে শিক্ষাবার্তা নামের একটি ফেসবুক পেজে গত ১ ফেব্রুয়ারি করা ‘ব্রেকিং নিউজ শিক্ষার্থীদের ৫ হাজার টাকা সহয়তা দেয়ার ঘোষণা, আবেদন শুরু’ শীর্ষক একটি পোস্ট খুঁজে পাওয়া যায়।

পোস্টটিতে বিস্তারিত কোনো তথ্য না থাকলেও এর মন্তব্যের ঘরে পেজটি থেকে করা একটি মন্তব্যে ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০২৪ সালে মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) ভর্তিকৃত ও অধ্যয়নরত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে ভর্তি সহায়তা দেওয়া হবে।’ শীর্ষক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

দাবিটির সত্যতা যাচাইয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ওয়েবসাইট অনুসন্ধানের মাধ্যমে গত ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত ‘মাধ্যমিক ও সমমান (৬ষ্ঠ-১০ শ্রেণি) এর ২০২৪ সালের ভর্তি সহায়তার বিজ্ঞপ্তি’ একটি বিজ্ঞপ্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তিটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণিতে) ২০২৪ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত/ অধ্যয়নরত অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিতকরণে অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের এই সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভর্তি সহায়তা পাওয়ার জন্যে শিক্ষার্থীদের ই-ভর্তি সহায়তা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যম অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
ভর্তি সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন শিক্ষার্থীরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বেসামরিক সব সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ‘জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫’ অনুযায়ী ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীর সন্তান আর্থিক এ অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পিতা, মাতা, অভিভাবকের বাৎসরিক আয় ২ লক্ষ টাকার কম হতে হবে।
এছাড়াও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, এতিম শিক্ষার্থী, ভূমিহীন পরিবারের সন্তান, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা সন্তানের সন্তান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ এবং দুস্থ পরিবারের সন্তান ভর্তির আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিটি থেকে আরও জানা যায়, আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই-বাছাই শেষে উপযুক্ত বিবেচিত হলে মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ৫ হাজার, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে ৮ হাজার এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ১০ হাজার করে ভর্তির জন্যে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

অর্থাৎ, বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক একটি স্পষ্ট যে মাধ্যমিকের সকল শিক্ষার্থী প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সহায়তা পাবে না।
মূলত, গত ২৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ওয়েবসাইটে মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে ২০২৪ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত/অধ্যয়নরত অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি সহায়তা প্রাপ্তির জন্যে অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি, ‘৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি: প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের ৫ হাজার টাকা সহায়তা আবেদন শুরু’ শীর্ষক দাবিতে একটি তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়। তবে রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে দেখা যায়, মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর ৫ হাজার টাকা সহায়তা পাওয়ার আলোচিত দাবিটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণিতে) ২০২৪ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত/ অধ্যয়নরত শুধুমাত্র অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিতকরণে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ৫ হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হবে।
প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ভর্তি সহায়তা প্রাপ্তির অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে যা আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি রাত ১১ টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত চলমান থাকবে।
সুতরাং, মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ৫ হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হবে দাবিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত তথ্যটি বিভ্রান্তিকর।
তথ্যসূত্র
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট Website: মাধ্যমিক-ও-সমমান-৬ষ্ঠ-১০-শ্রেণি-এর-২০২৪-সালের-ভর্তি-সহায়তার-বিজ্ঞপ্তি
- Rumor Scanner’s Own Analysis