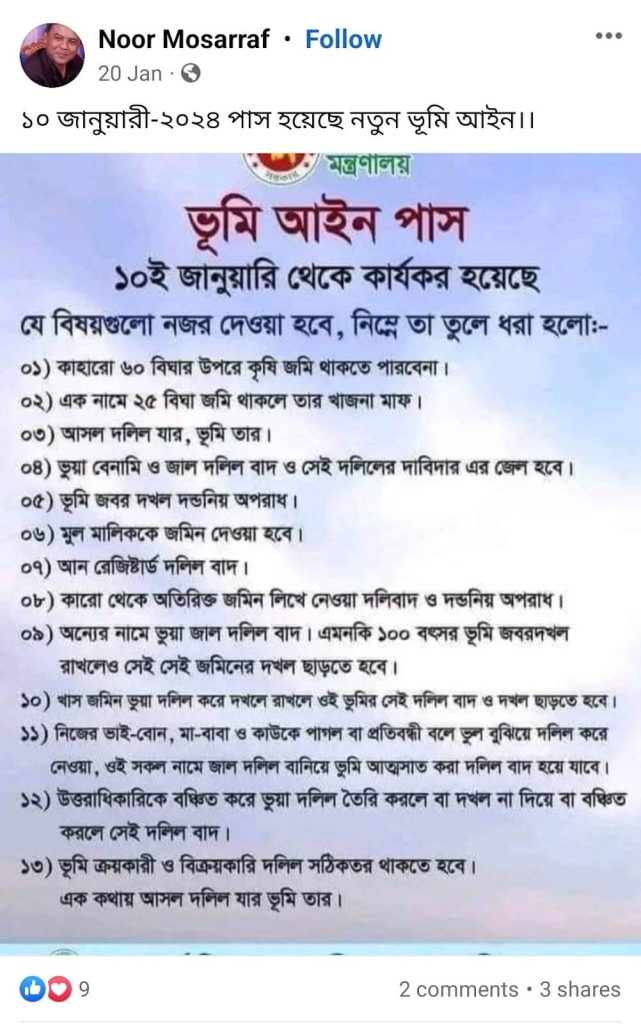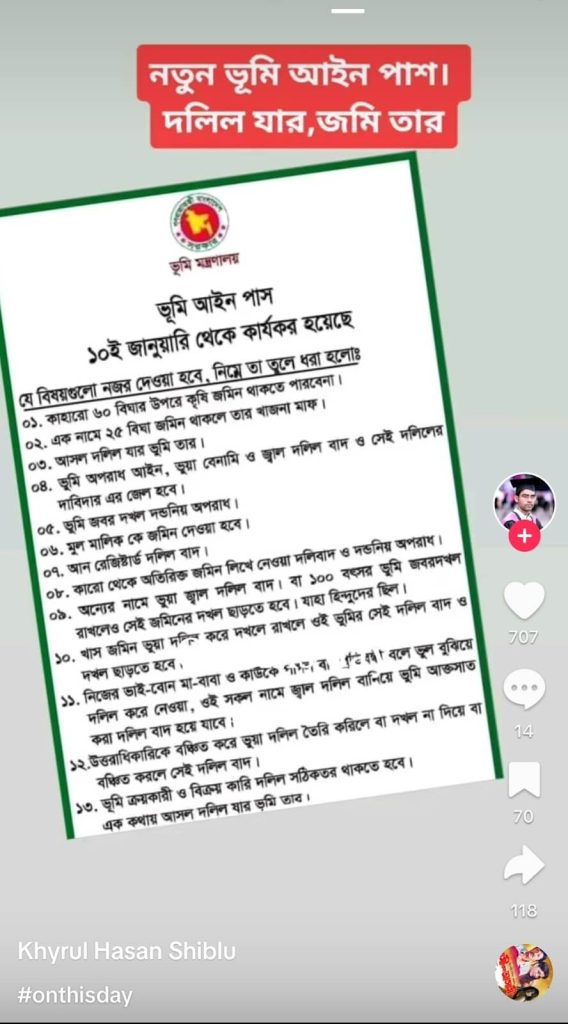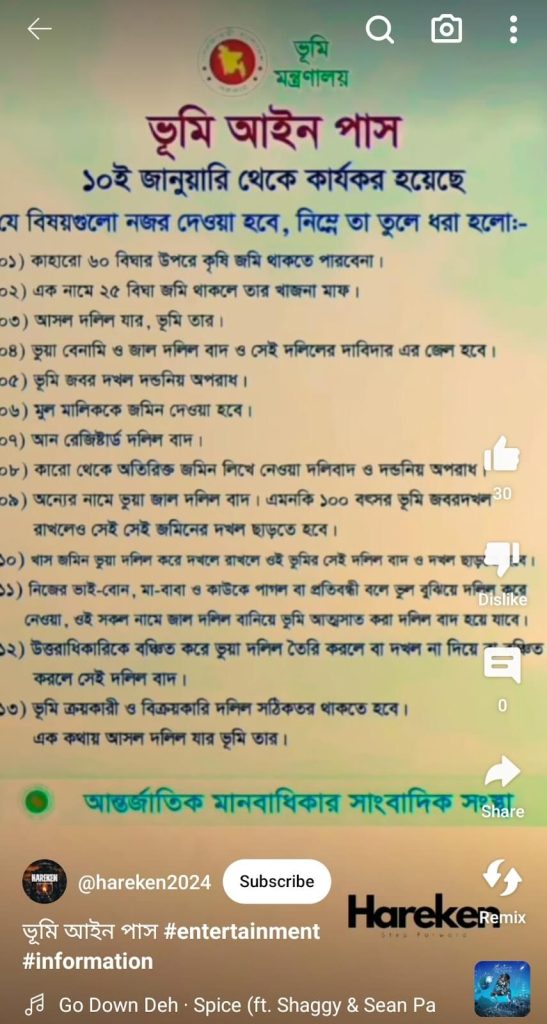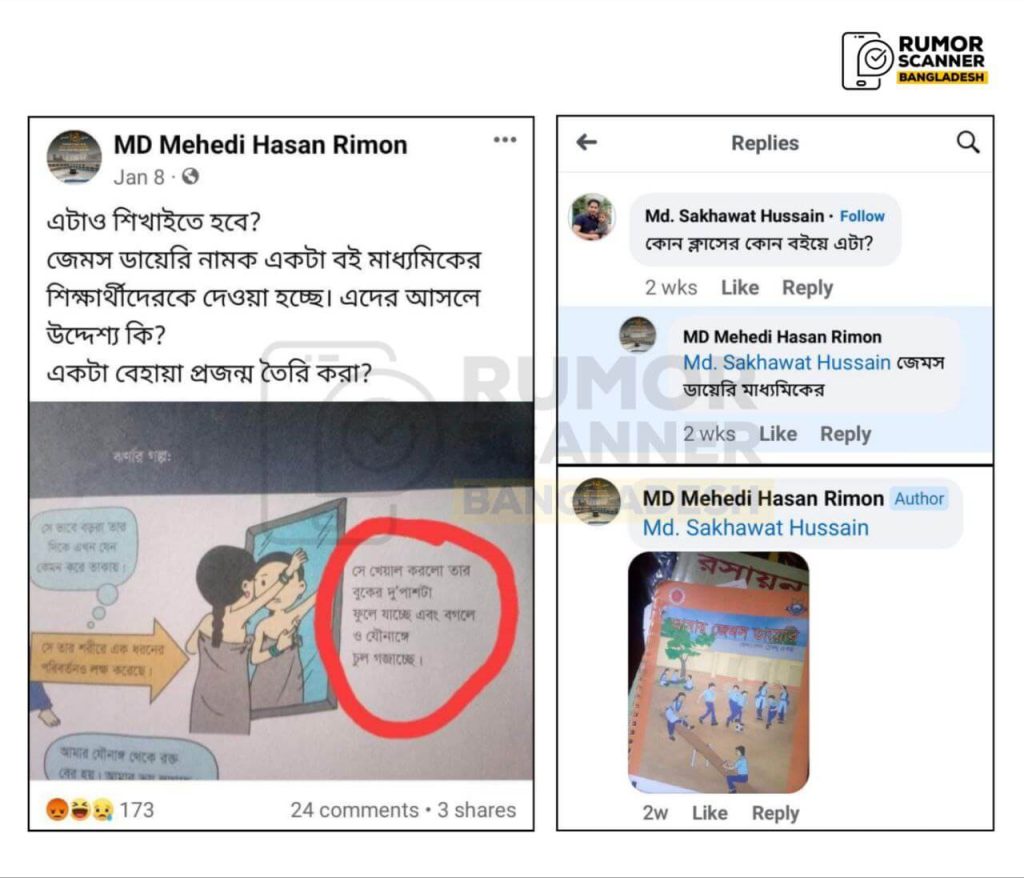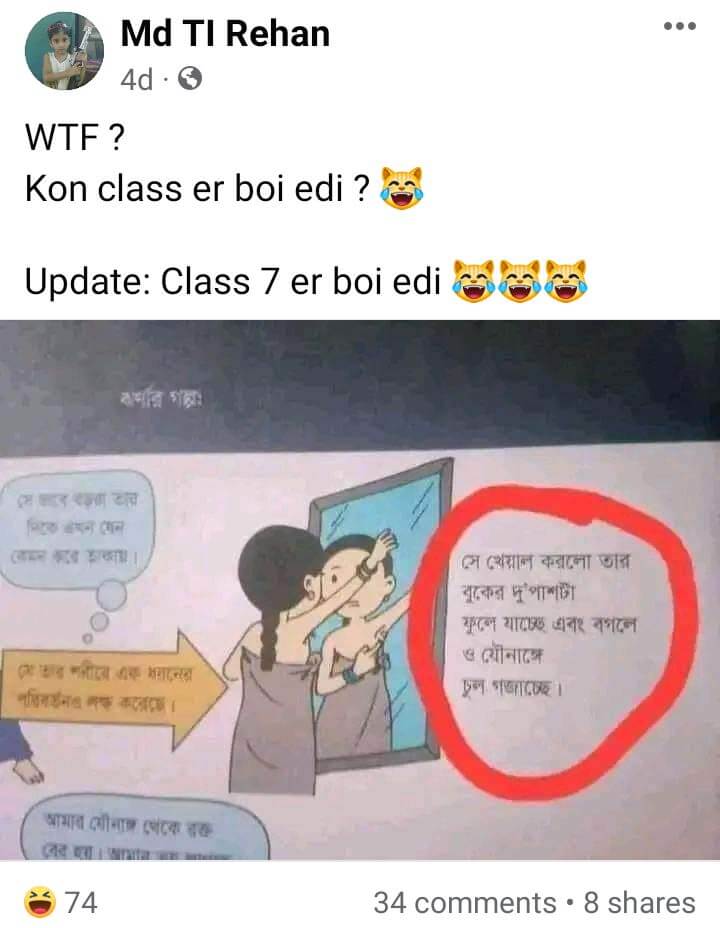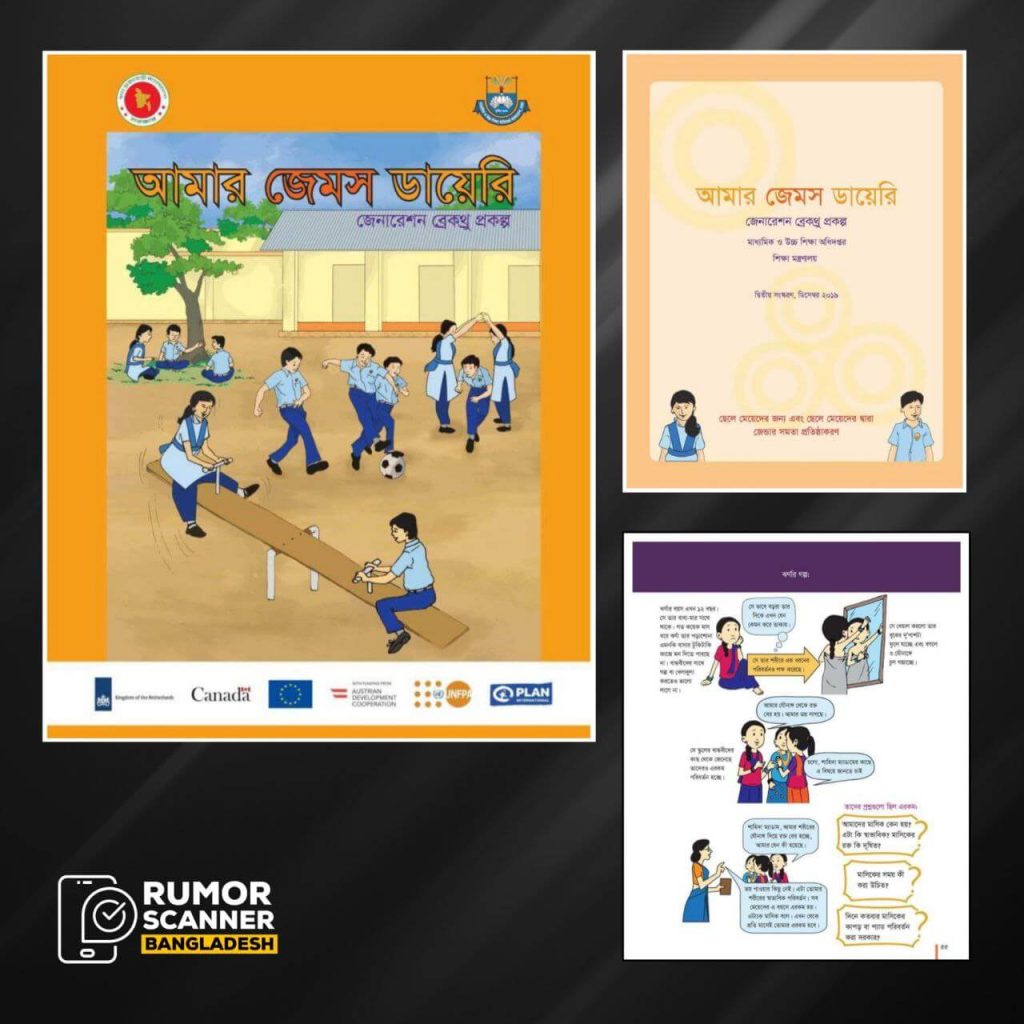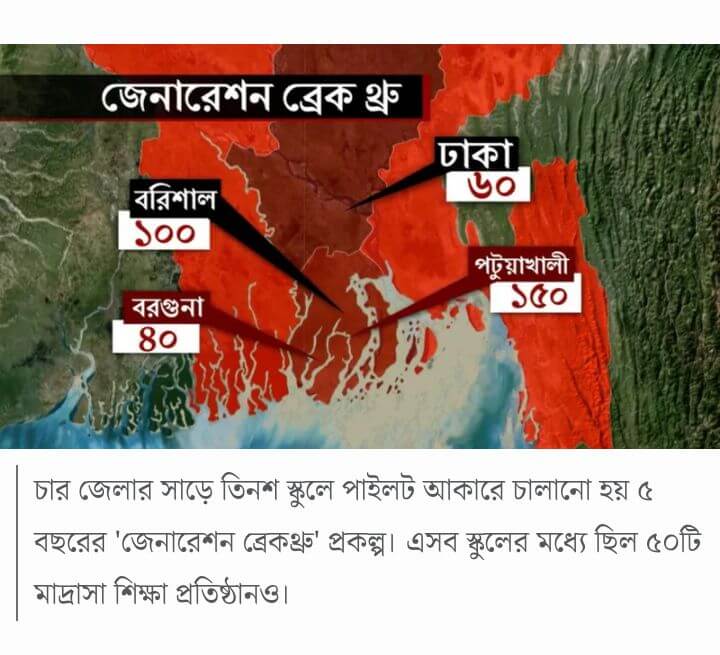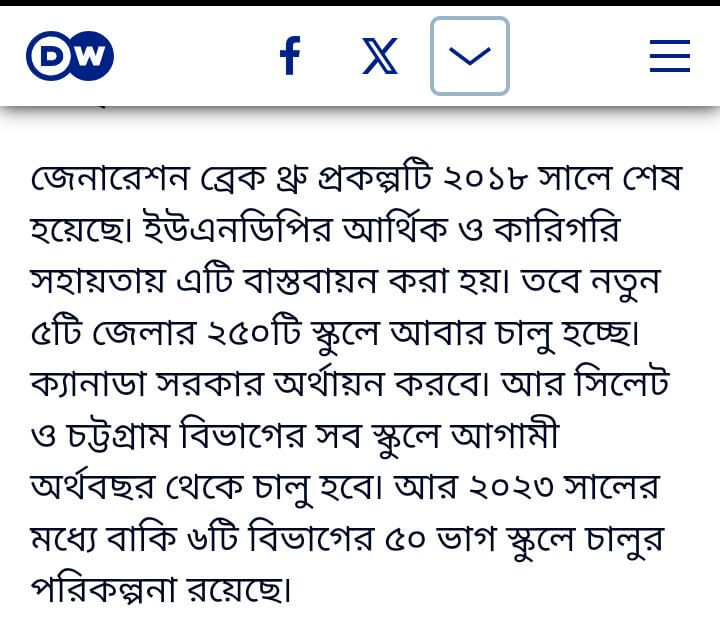গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ২২২টি সংসদীয় আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। তবে গত ২৩ জানুয়ারি ভিডিও শেয়ারিং প্লাটফর্ম ইউটিউবে “সংসদেই হাসিনার পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা। Caretaker Government” শীর্ষক শিরোনাম এবং “সংসদে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ঘোষণা” শীর্ষক থাম্বনেইলে একটি ভিডিও প্রচার করা হয়েছে।

ইউটিউবে প্রচারিত ভিডিওটি দেখুন এখানে (আর্কাইভ)।
ফ্যাক্টচেক
রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ঘোষণা দেননি বরং অধিক ভিউ পাওয়ার আশায় চটকদার শিরোনাম ও থাম্বনেইল ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার পুরোনো কিছু ভিডিও ক্লিপ যুক্ত করে আলোচিত ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে।
অনুসন্ধানের শুরুতে আলোচিত ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ করে রিউমর স্ক্যানার টিম। উক্ত ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুইটি ভিডিও ক্লিপ এবং আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির যুগ্ম সদস্য সচিব ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের একটি ভিডিও দেখানো হয়। তবে ভিডিওর কোথাও শেখ হাসিনা কর্তৃক পুনরায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার দাবির স্বপক্ষে কোনো তথ্য বা দৃশ্য দেখা যায়নি।
পরবর্তীতে ভিডিওটিতে প্রচারিত ভিডিও ক্লিপগুলো পৃথকভাবে যাচাই করেছে রিউমর স্ক্যানার টিম।
ভিডিও যাচাই – ০১
আলোচিত ভিডিওটিতে দেখানো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম ভিডিও ক্লিপটির অনুসন্ধানে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে এনটিভি নিউজের ইউটিউব চ্যানেলে ২০২৩ সালের ১৫ মে “নির্বাচন আসছে, তাতে ভয়ের কিছু নেই : প্রধানমন্ত্রী। PM । NTV News” শীর্ষক শিরোনামে একটি ভিডিও প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়।

উক্ত ভিডিও প্রতিবেদনের একটি অংশের সাথে আলোচিত ভিডিওর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুটেজ অংশের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
ভিডিওটিতে গত ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০২৩ সালের ১৫ মে গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সরকার কোনো ‘ভয়ে নেই’ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্বাচন আসছে বলে ভয় পাবো! কেন ভয় পাবো! আমি জনগণের জন্য কাজ করেছি, জনগণ যদি ভোট দেয় আছি, না দিলে নাই। ভিডিও প্রতিবেদনের এই অংশটিই আলোচিত ভিডিওটিতে যুক্ত করা হয়েছে।
ভিডিও যাচাই – ০২
আলোচিত ভিডিওটিতে থাকা দ্বিতীয় ভিডিওটির অনুসন্ধানে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে চ্যানেল আই নিউজের ইউটিউব চ্যানেলে ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর “২১টি অঙ্গিকার নিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার” শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

উক্ত ভিডিওর একটি অংশই আলোচিত ভিডিওটিতে যুক্ত করা হয়েছে।
ভিডিওটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হলে সমৃদ্ধ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ‘২১ টি বিশেষ অঙ্গীকার ‘বাস্তবায়ন করবে বলে নির্বাচনী ইশতেহার দেন।
ভিডিও যাচাই – ০৩
আলোচিত ভিডিওটির সর্বশেষ অংশে এবি পার্টির যুগ্ম সদস্য সচিব ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের একটি ভিডিও দেখানো হয়। উক্ত ভিডিওটির অনুসন্ধানে ‘ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ -Barrister Fuaad’ নামক ইউটিউব চ্যানেলে গত ২২ জানুয়ারি “যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা কিভাবে কাজ করে” শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।

এই ভিডিওটির একটি অংশই আলোচিত ভিডিওটিতে ব্যবহার করা হয়েছে।
উক্ত ভিডিওতে ব্যারিস্টার ফুয়াদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন।
অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়নি।
পাশাপাশি, গণমাধ্যম কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচন গ্রহণের ঘোষণার দাবির সত্যতা পাওয়া যায়নি।
মূলত, ০৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ২৯৮ আসনের ফলাফলে ২২২ টি আসন লাভ করে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। তবে গত ২৩ জানুয়ারি Sabai Sikhi নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে ‘সংসদে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ঘোষণা’ শীর্ষক দাবি সম্বলিত একটি ভিডিও প্রচার করা হয়েছে। রিউমর স্ক্যানার টিম অনুসন্ধান করে দেখেছে, উক্ত দাবিটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন প্রেক্ষাপটের পুরোনো কয়েকটি ভিডিও’র সাথে চটকদার শিরোনাম ও থাম্বনেইল যুক্ত করে আলোচিত ভিডিওটি প্রচার করা হয়েছে।
সুতরাং, প্রধান শেখ হাসিনা কর্তৃক ক্ষমা চেয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছেদাবিতে ইন্টারনেটে প্রচারিত তথ্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।
তথ্যসূত্র
- NTV News : নির্বাচন আসছে, তাতে ভয়ের কিছু নেই: প্রধানমন্ত্রী। PM । NTV News
- Channel i Online : ২১টি অঙ্গিকার নিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার
- YouTube Channel : ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ -Barrister Fuaad