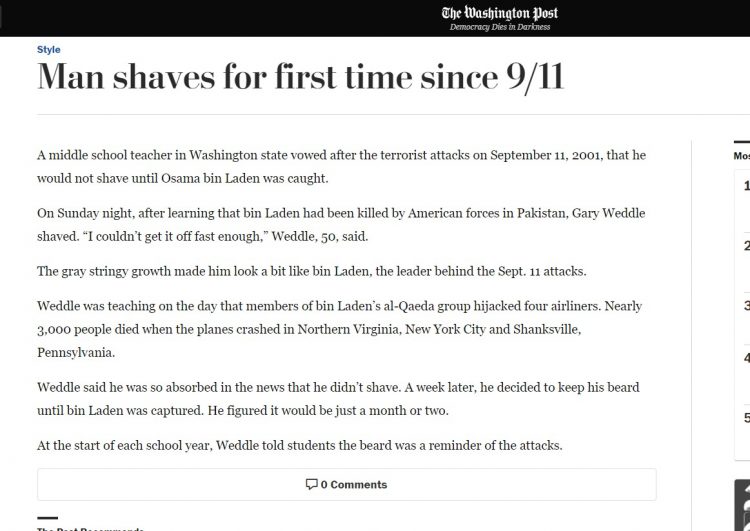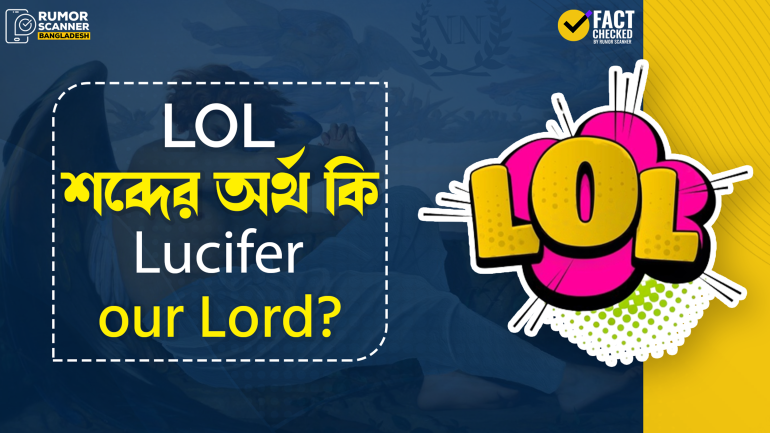সম্প্রতি “এখন থেকে আর চার্জ দিতে হবে না, এসে গেলো সোলার রিকশা” শীর্ষক শিরোনামে একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।


ভাইরাল হওয়া কিছু ফেসবুক পোস্ট দেখুন এখানে, এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে।
ফ্যাক্টচেক
রিভার্স ইমেজ সার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে রিউমর স্ক্যানার টিম নিশ্চিত হয়েছে সোলার রিকশার ছবিটি বাংলাদেশের নয় বরং ভারতের।
মূলত ২০১৯ সালের ১৯শে জুলাই ভারতের আইআইটি দিল্লি ক্যাম্পাসে সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রনিকস লিমিটেডের পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসেবে রিকশা চালকদের হাতে স্মার্ট সোলার রিকশা তুলে দেওয়া হয় এবং আইআইটি এর টুইটার একাউন্টেও উক্ত বিষয়ে একাধিক ছবির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।
Smart Solar Rickshaws handed over to rickshaw pullers in IITD campus by Central Electronics Limited under CSR program as part of their pilot project. These rickshaws run with combination of Solar, Human & Conventional Electrical Power (optional) and will ply inside the campus. pic.twitter.com/ltYLLQlGBY
— IIT Delhi (@iitdelhi) July 19, 2019
এছাড়াও ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোতেও তৎকালীন সময়ে এই বিষয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিলো। Times of India এর “Solar rickshaws make debut on IIT-Delhi campus” শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখুন এখানে।


অথাৎ, ভারতের আইআইটি দিল্লি ক্যাম্পাসে রিকশা চালকদের হাতে স্মার্ট সোলার রিকশা তুলে দেওয়ার ছবিকে বাংলাদেশে সোলার রিকশার আগমন দাবীতে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর।
[su_box title=”True or False” box_color=”#f30404″ radius=”0″]

- Claim Review: আর চার্জ দিতে হবেনা, দেশে চলে এসেছে সোলার রিকশা
- Claimed By: Facebook Posts
- Fact Check: Misleading
[/su_box]