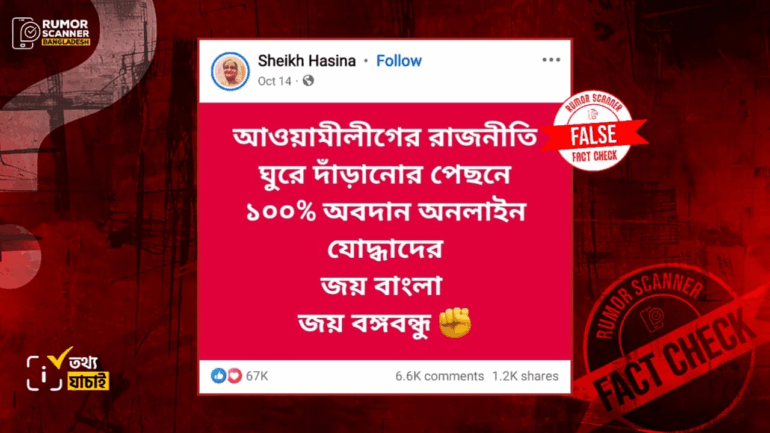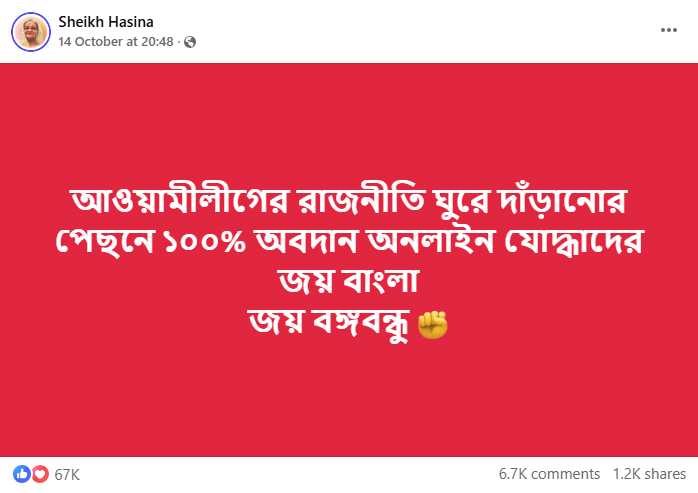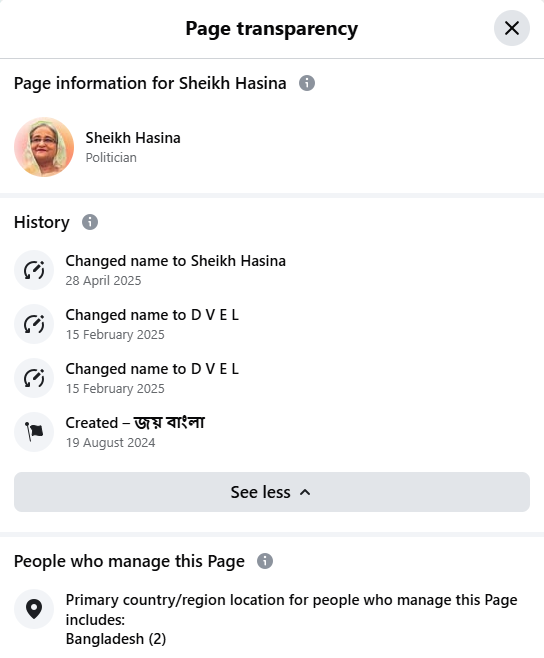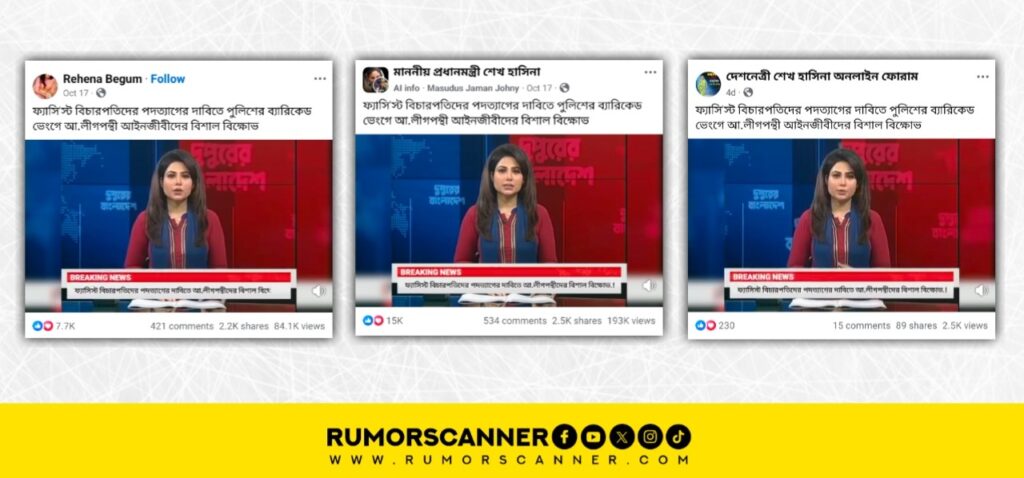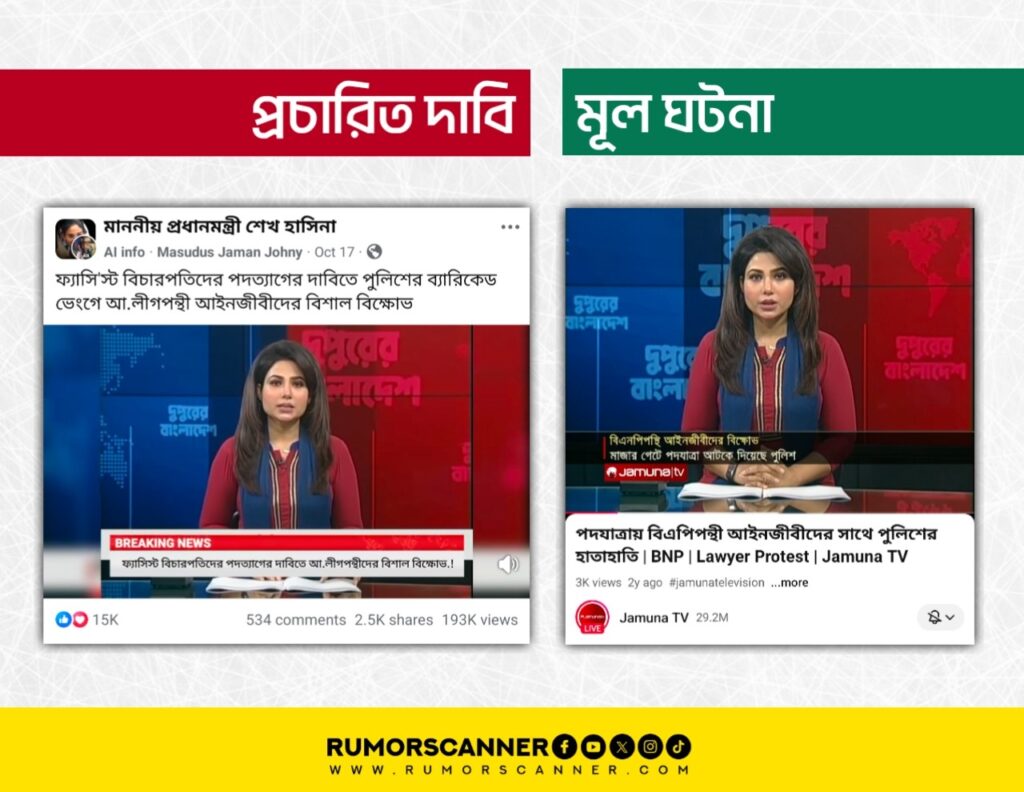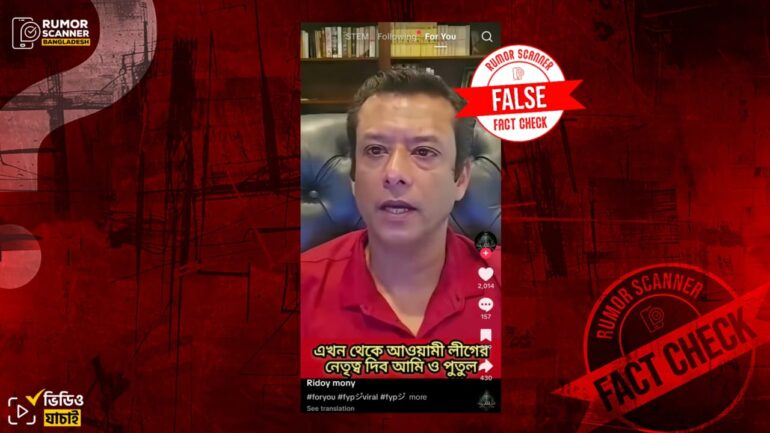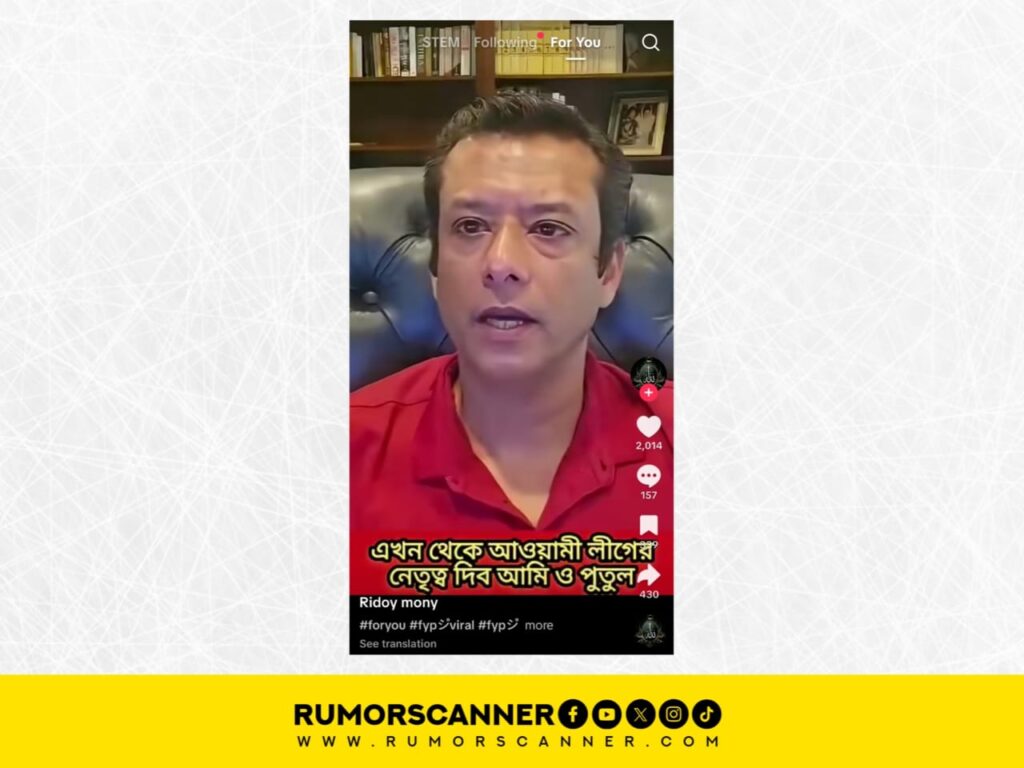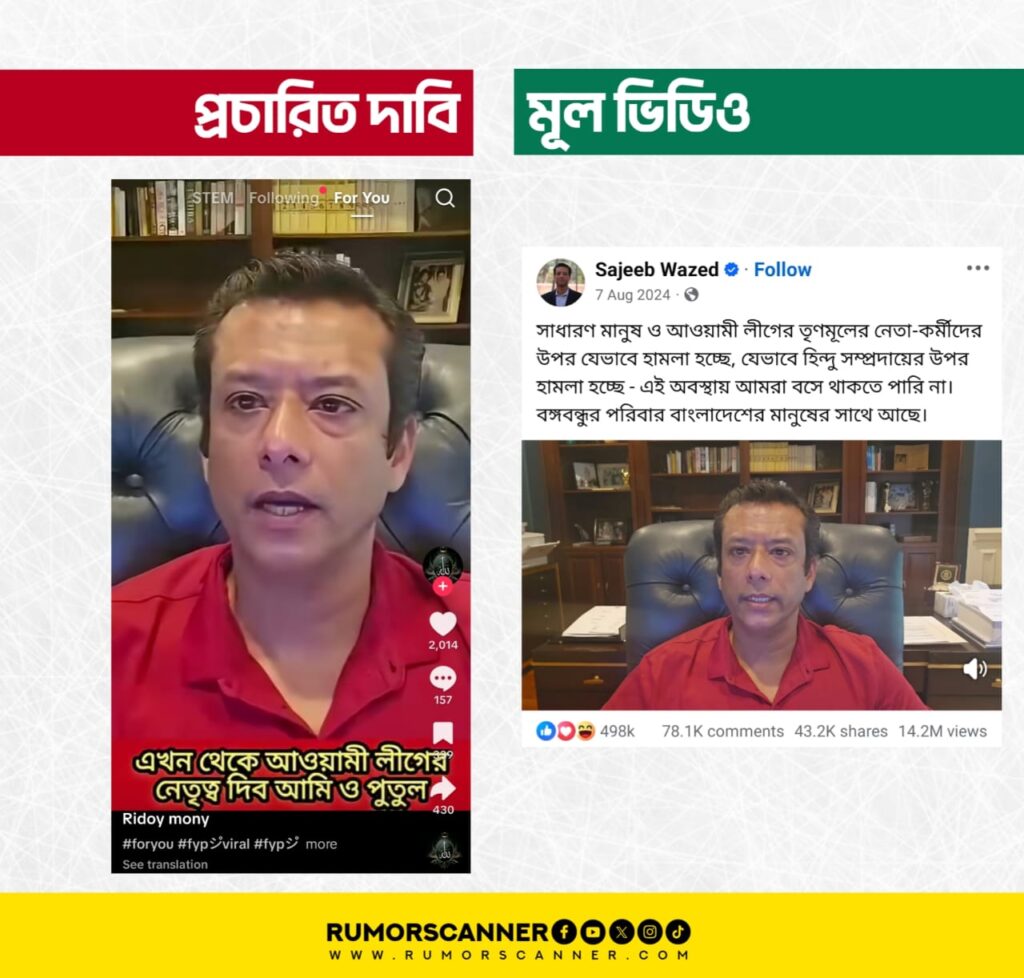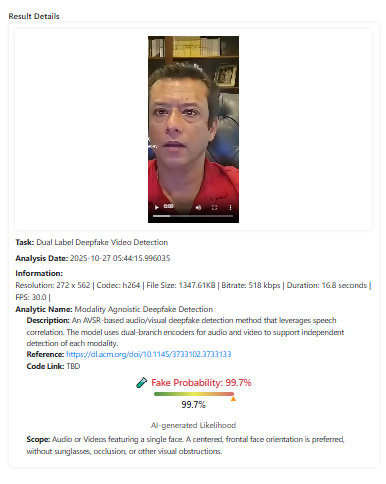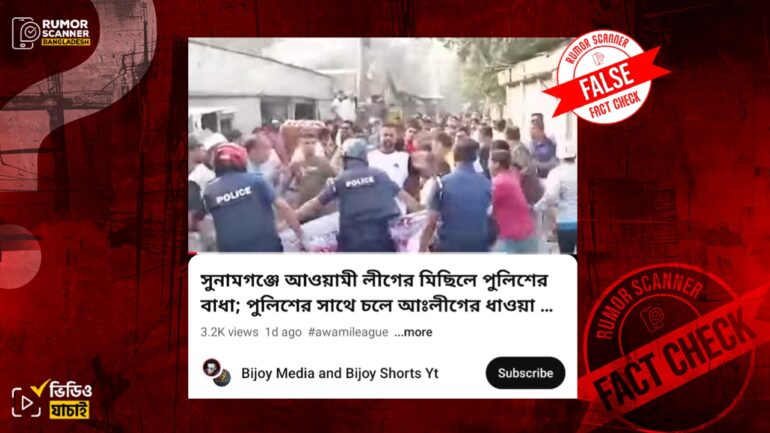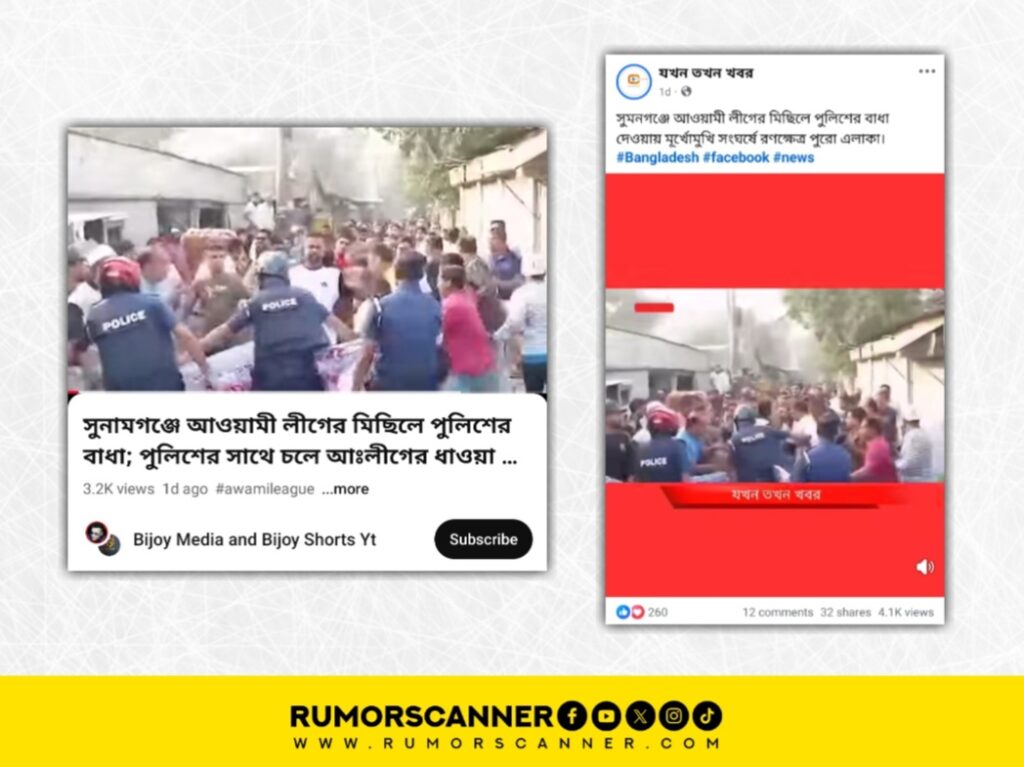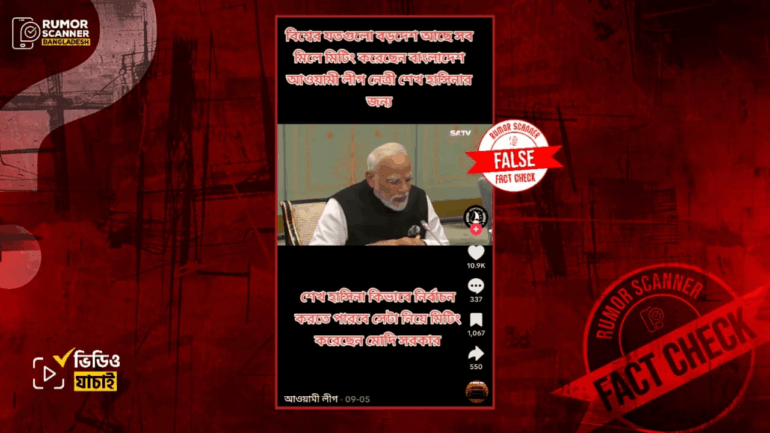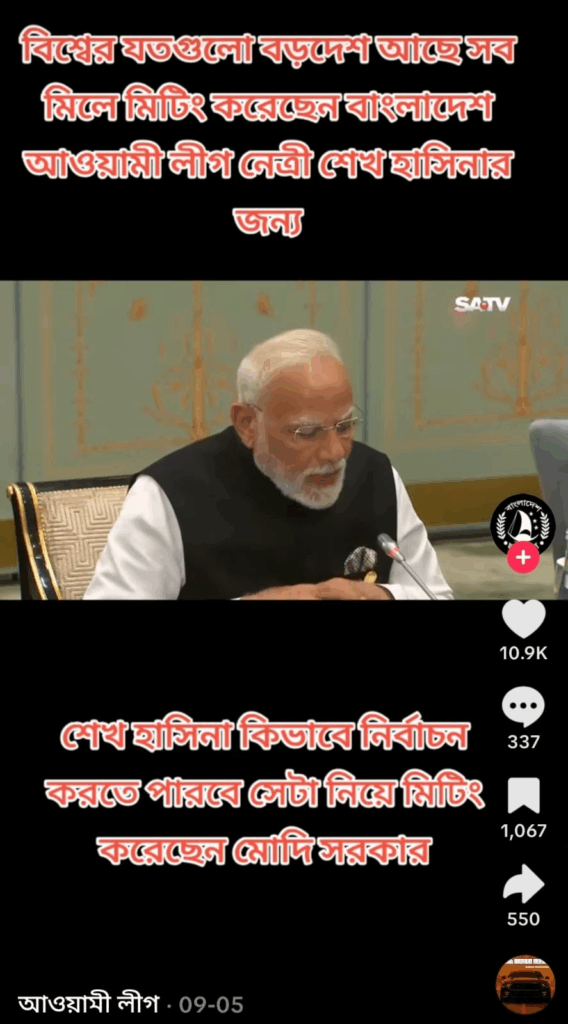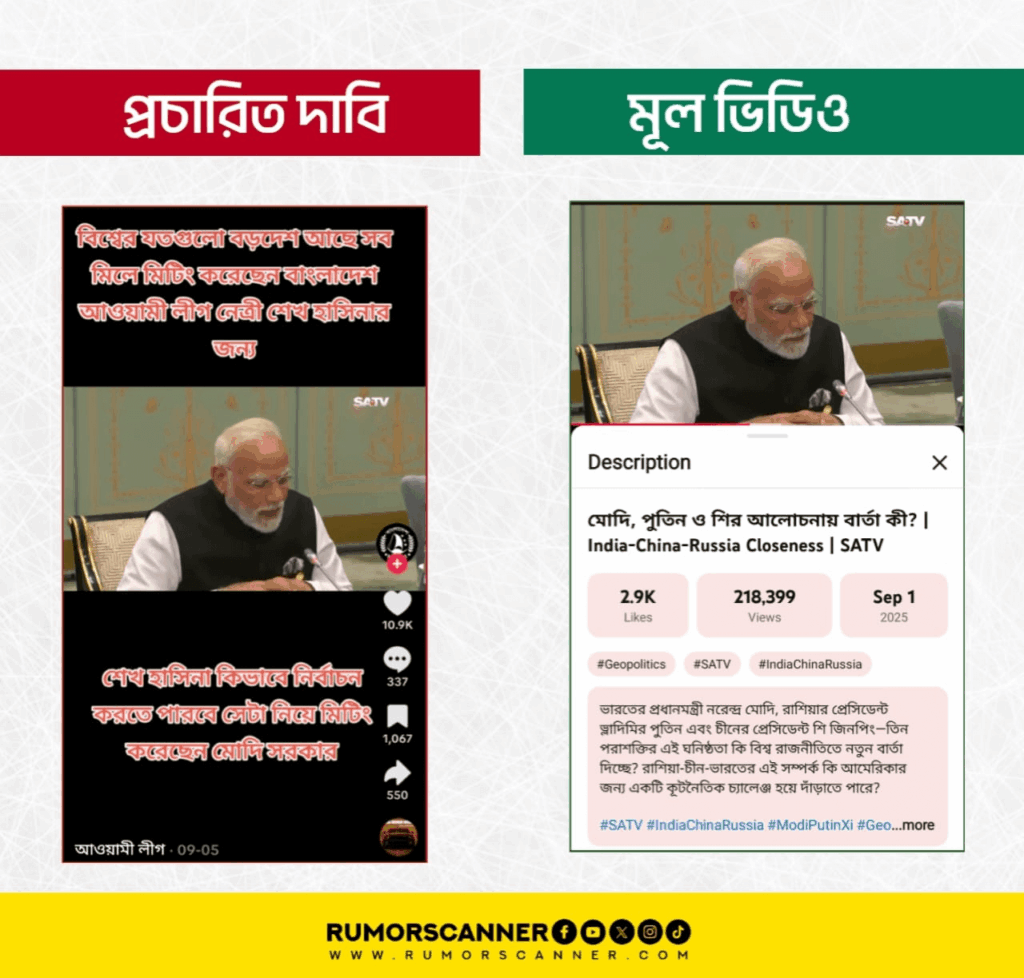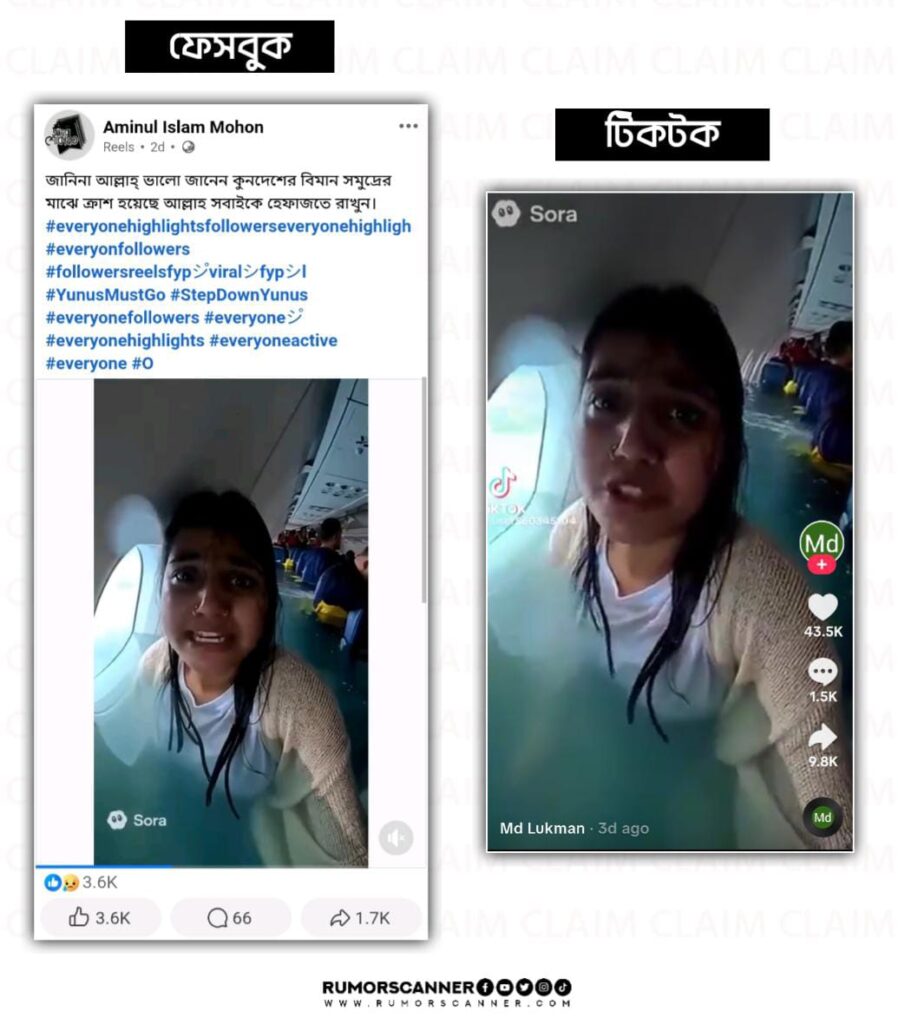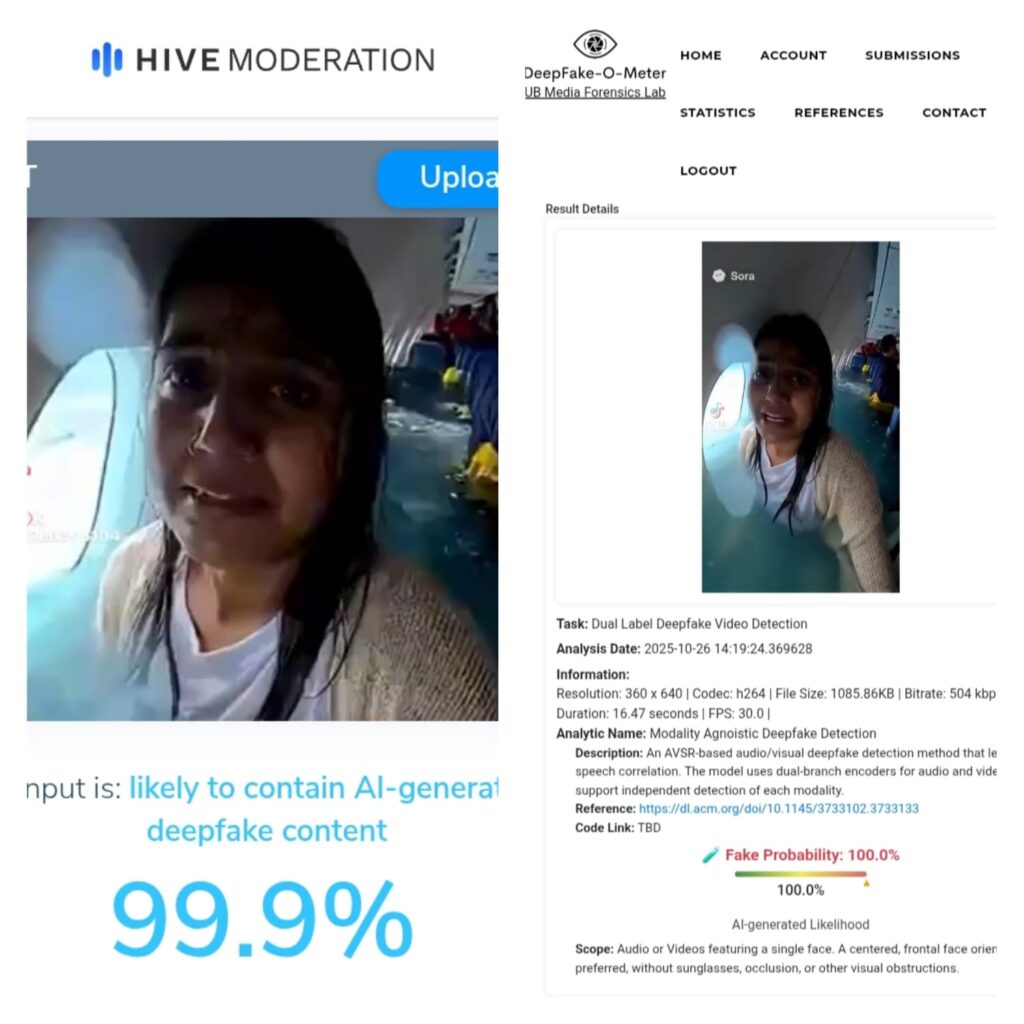সম্প্রতি ‘২৪ এর স্বাধীন বাংলাদেশে আমার বোনদের নিরাপদ নেই ইউনুস এর শাসন আমল কেমন জনগণ দেখুন।’ ক্যাপশনে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। ভিডিওটিতে জনসমক্ষে একজন পুরুষকে এক নারীর ওপর ধারালো অস্ত্র দ্বারা হামলা করতে দেখা যায়।

উক্ত দাবিতে ফেসবুকে প্রচারিত পোস্ট দেখুন এখানে (আর্কাইভ)৷
এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়া অবধি ফেসবুকে প্রচারিত সর্বাধিক ভাইরাল ভিডিওটি প্রায় ৪২ হাজার বার দেখা হয়েছে, এটিতে প্রায় ১ হাজার পৃথক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে এবং ভিডিওটি ৫ শত বার শেয়ার করা হয়েছে।
ফ্যাক্টচেক
রিউমর স্ক্যানার টিমের অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রকাশ্যে এক নারীর ওপর হামলা দাবিতে প্রচারিত ভিডিওর ঘটনাটি বাংলাদেশে ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হামলার শিকার হওয়ার ভিডিওকে বাংলাদেশের ঘটনা দাবিতে প্রচার করা হয়েছে৷
এ বিষয়ে অনুসন্ধানে Karnataka portfolio নামক ফেসবুক পেজে গত ২৬ অক্টোবর প্রকাশিত পোস্টে একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়। উক্ত ভিডিওর কিছু অংশের সাথে আলোচিত ভিডিওটির দৃশ্যাবলীর সাদৃশ্য রয়েছে।
উক্ত ভিডিওটির ক্যাপশন থেকে জানা যায়, ভিডিওর ঘটনাটি বিজয়পুরার সিন্দাগি শহরে ঘটেছে, যেখানে যমনাপ্পা মাদার নামক ৬০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে তার ৫০ বছর বয়সী স্ত্রী অনসূয়া মাদারকে চাপাতি দিয়ে আক্রমণ করেন। পারিবারিক কলহের জেরে এই আক্রমণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে৷
উল্লিখিত তথ্যাবলীর সূত্র ধরে ভারতীয় গণমাধ্যম NDTV এর ওয়েবসাইটে গত ২৪ অক্টোবর ‘Man, 60, Attacks Wife With Machete On A Busy Road In Karnataka’ শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়। উক্ত প্রতিবেদনে যুক্ত ছবির সাথে আলোচিত ভিডিওটির দৃশ্যের মিল রয়েছে।

উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ভারতের কর্ণাটকের বিজয়পুর জেলার সিন্দাগি শহরে ৬০ বছর বয়সী যমনাপ্পা মাদার তার ৫০ বছর বয়সী স্ত্রী অনুসুয়া মাদারের উপর একটি ব্যস্ত রাস্তায় মাচেট (ধারালো হাতিয়ার) দিয়ে হামলা চালান। ভিডিওতে দেখা যায়, শাড়ি পরা অনুসুয়াকে যমনাপ্পা তাড়া করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বারবার আঘাত করছেন। এক পর্যায়ে অনুসুয়া রাস্তায় পড়ে গেলেও হামলা চালানো বন্ধ হয়নি। পরে অন্য একজন ব্যক্তি যমনাপ্পাকে কাঠের লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। উভয়কে সিন্দাগি তালুক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।
এ বিষয়ে আরেক ভারতীয় গণমাধ্যম NEWS9 এর ইউটিউব চ্যানেলে গত ২৫ অক্টোবর ‘Vijayapura Man Brutally Assaults Wife With Machete’ শিরোনামে প্রকাশিত ভিডিও প্রতিবেদন থেকেও একই তথ্য জানা যায়।
অর্থাৎ, আলোচিত ভিডিওর ঘটনাটি বাংলাদেশে ঘটেনি।
সুতরাং, বাংলাদেশে প্রকাশ্যে এক নারীর ওপর হামলার ভিডিও দাবিতে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর হামলার ভিডিও প্রচার করা হয়েছে; যা মিথ্যা।
তথ্যসূত্র
- Karnataka portfolio – Facebook Post
- ND TV – Man, 60, Attacks Wife With Machete On A Busy Road In Karnataka
- NEWS9 Live – Vijayapura Man Brutally Assaults Wife With Machete