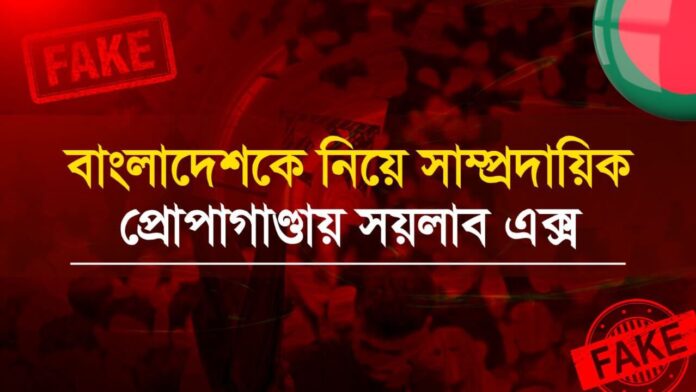চলতি বছরের পাঁচ জুন বাংলাদেশের হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ কোটা বাতিল করে ২০১৮ সালে সরকারের জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিল করে দেয়। এই এক ইস্যুতে নানান ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি হিসেবে ঠিক দুই মাসের মাথায় সরকার পতনের মতো ঘটনা দেখে বাংলাদেশ। তবে এর আগেই সংঘাত আর সংঘর্ষের ভয়াবহ রূপ সামনে আসে, আসে বহু হতাহতের খবরও। ০৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ শাসনামলের অবসান ঘটে৷ সরকারবিহীন পরের তিনদিনেও দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক হামলা হয়েছে। হত্যা, ভাংচুর, পুড়িয়ে দেওয়া, লুটপাটের অসংখ্য খবরও প্রকাশ্যে আসে। হামলা হয় বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের বাসা এবং স্থাপনায়ও। এসব ঘটনাবলির মধ্যেই সাম্প্রদায়িক ভুল তথ্য এবং অপতথ্যের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যম হয়ে ওঠেছে মাইক্রোব্লগিং সাইট হিসেবে পরিচিত প্লাটফর্ম এক্স (সাবেক টুইটার)।
রিউমর স্ক্যানার ইনভেস্টিগেশন ইউনিট গেল এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ করে এক্সে এমন ৫০টি অ্যাকাউন্ট খুঁজে বের করেছে, যেগুলোতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির বিভিন্ন ছবি, ভিডিও এবং তথ্যকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। এসব অ্যাকাউন্টের প্রতিটির অন্তত একটি পোস্টে সাম্প্রদায়িক অপতথ্য ও ভুল তথ্য প্রচারের প্রমাণ পেয়েছে রিউমর স্ক্যানার। এসব অ্যাকাউন্টে গত ০৫ থেকে ১৩ আগস্টের মধ্যে প্রচারিত উক্ত পোস্টগুলো ১ কোটি ৫৪ লাখের বেশি বার দেখা হয়েছে। রিউমর স্ক্যানার ইনভেস্টিগেশন ইউনিট বিশ্লেষণ করে দেখেছে, ভুয়া এবং অপতথ্য ছড়ানো এসব অ্যাকাউন্টধারীর ৭২ শতাংশই ভারতে থাকেন বলে উল্লেখ করেছেন। অ্যাকাউন্টধারীদের মধ্যে দায়িত্বশীল অনেক ব্যক্তিও রয়েছেন। এমনকি ভারতের একাধিক মূল ধারার গণমাধ্যমেও এসব ভুয়া তথ্য প্রচার করা হয়েছে।
সাম্প্রদায়িক ভুয়া ও অপতথ্যের ধরণ
গত ০৭ জুলাই বগুড়ায় জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনারই একটি ভিডিও সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গত ০৯ আগস্ট ভারতের একটি এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করে দাবি করা হয়, “বাংলাদেশের হিন্দু নারী ও শিশুদের একটি ক্যাম্পে জিহাদিরা বোমা দিয়ে হামলা চালিয়ে শত শত নারীকে হত্যা করার দৃশ্য।” রিউমর স্ক্যানার ইনভেস্টিগেশন ইউনিট যে ৫০টি অ্যাকাউন্টের একটি করে পোস্টকে এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে ১৩টি পোস্টেই ভিন্ন ঘটনাকে এমন সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয়েছে।
তবে সবচেয়ে বেশি ঘটেছে মুসলিম ব্যক্তিকে হিন্দু দাবিতে প্রচারের ঘটনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের অভিনেত্রী আজমেরী বাঁধনের প্রসঙ্গ। তাকে হিন্দু দাবি করে একটি ভিডিওর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে, “বাংলাদেশে হিন্দু নারীর কান্না করে বক্তৃতা দেওয়ার দৃশ্য।” বাঁধন নিজেই বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এমন আরো ১৭টি ঘটনার প্রমাণ পেয়েছে রিউমর স্ক্যানার ইনভেস্টিগেশন ইউনিট, যা ধরণ অনুযায়ী সর্বোচ্চ (৩৬ শতাংশ)।
এছাড়া, ভিন্ন ঘটনার পুরোনো ভিডিও, মুসলিমদের স্থাপনায় সাম্প্রতিক হামলাকে হিন্দুদের স্থাপনায় হামলা দাবি, ভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে হিন্দুদের স্থাপনায় হামলার দাবি, রাজনৈতিক স্লোগানের বক্তব্যকে ভিন্ন দাবি, স্ক্রিনশট বিকৃতি, ভুয়া বক্তব্য, বিএনপির নামে ভুয়া টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টের বরাতে ভুল তথ্য এবং হিন্দু নিহতের সংখ্যা নিয়ে ভুয়া দাবির মাধ্যমে এসব অর্ধশতাধিক ভুয়া তথ্যের ব্যাপক প্রচার লক্ষ্য করেছে রিউমর স্ক্যানার।
প্রচারিত পোস্টগুলোর ক্ষেত্রে ভুয়া তথ্যের প্রচারে ৮০ শতাংশ (৪০টি) ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়েছে ভিডিও ফুটেজ। এসব ভিডিও ফুটেজের মধ্যে ১৫টি ০৫ আগস্টের পূর্বের ভিন্ন ঘটনার। বাকিগুলো সরকার পতন পরবর্তী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার হলেও এসব ফুটেজকে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক ভুয়া তথ্যের প্রচারে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া, ১৬ শতাংশ ক্ষেত্রে ছবি ও স্ক্রিনশট এবং বাকি চার শতাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে ছবি/ভিডিও বিহীন স্ট্যাটাস।
অর্ধশতাধিক অ্যাকাউন্টে সাম্প্রদায়িক প্রোপাগান্ডার নজির
রিউমর স্ক্যানার ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বাংলাদেশ নিয়ে সাম্প্রদায়িক ভুল এবং অপতথ্য যে ৫০টি এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচার করা হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে ৩৬টি অ্যাকাউন্টেরই লোকেশন হিসেবে ভারতের নাম উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, লোকেশন হিসেবে হাঙ্গেরি, যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, সুইডেন, সোমালিয়া, থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশ উল্লেখ রয়েছে একটি করে অ্যাকাউন্টে। এর বাইরে কোনো লোকেশনই উল্লেখ করেনি এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা পাঁচটি।
এসব অ্যাকাউন্টে নিয়মিত ভিত্তিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন তথ্য, ছবি, ভিডিওকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। অ্যাকাউন্টগুলো দীর্ঘ বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুধু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিই নয়, এসব অ্যাকাউন্টে বেশ কয়েক বছর যাবতই নানা ধরণের ভুল তথ্য প্রচার হয়ে আসছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে জড়িয়েই এসব অ্যাকাউন্টে সময়ে সময়ে ভুল তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। এসবের জেরে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ফ্যাক্টচেকারদের কাছেও অ্যাকাউন্টগুলো বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেছে। রেটিং বা কার্যকরী ফ্যাক্টচেকিং প্রোগ্রাম না থাকা এবং কমিউনিটি গাইডলাইনের মতো দুর্বল পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এসব অ্যাকাউন্ট বছরের পর বছর ধরে অপতথ্য প্রচারের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠেছে।
অপপ্রচারে দায়িত্বশীল ব্যক্তি থেকে গণমাধ্যম
সম্প্রতি এক হিন্দু ব্যক্তি তার নিখোঁজ পুত্রের সন্ধান দাবিতে মানববন্ধন করছে এমন দৃশ্য দাবি করে একটি ভিডিও ভারতের মূলধারার অন্তত তিন গণমাধ্যম এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল (ANI), এনডিটিভি, মিরর নাউ এর এক্স অ্যাকাউন্টে প্রচার করা হয়। তবে রিউমর স্ক্যানার যাচাই করে দেখেছে, উক্ত ব্যক্তি মুসলিম। বাবুল হাওলাদার নামে এই ব্যক্তি ২০১৩ সাল থেকে নিখোঁজ থাকা তার ছেলের সন্ধান দাবিতে এই মানববন্ধনে অংশ নিয়েছিলেন৷ সাম্প্রদায়িক অপতথ্যের এমন প্রচারে ভারতীয় আরো একাধিক গণমাধ্যম এবং গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে রিউমর স্ক্যানার৷ এই তালিকায় আরো আছে জি নিউজ মধ্যপ্রদেশ এবং নিউজ টুয়েন্টিফোর নামে গণমাধ্যমের এক্স অ্যাকাউন্ট।
ভারতের আরেক সুপরিচিত গণমাধ্যম অপিইন্ডিয়া এর প্রধান সম্পাদক নুপুর শর্মাকেও তার এক্স অ্যাকাউন্টে নিয়মিত বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক অপতথ্য ছড়াতে দেখেছে রিউমর স্ক্যানার ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। ১১ আগস্ট প্রকাশিত তার একটি এক্স পোস্টকে ভুয়া তথ্য হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে জানানোর পর তিনি রিউমর স্ক্যানারের একজন টিম মেম্বারকে এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে ব্লক করেন৷
সাম্প্রদায়িক গুজব প্রচারে ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশের একাধিক দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও ভূমিকা থাকার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ইরাকি বংশোদ্ভূত সালওয়ান মোমিকা একাধিকবার প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরআন পুড়িয়ে বিতর্ক ও সমালোচনার সৃষ্টি করেন, হয়েছেন গণমাধ্যমের শিরোনাম। এই ব্যক্তিকে তার এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়মিত বাংলাদেশকে জড়িয়ে সাম্প্রদায়িক অপতথ্য প্রচারের প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া, পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক লেগ স্পিনার দানিশ কানেরিয়াকে তার এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে ক্রিকেটার লিটন দাসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে দাবিতে একটি ভিডিও ফুটেজ শেয়ার করতে দেখা গেছে। আদতে এটি ছিল মাশরাফির বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ফুটেজ। লিটনের বাড়িতে কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি।
সাম্প্রদায়িক গুজবের নেপথ্যে
এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে সাম্প্রদায়িক কোনো মৃত্যুর খবর বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া যায়নি। তবে এটা সত্যি যে, সাম্প্রদায়িক হামলার বেশ কিছু ঘটনা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আবহের মধ্যে এমন হামলাগুলোকে সামনে রেখে এক্সে সাম্প্রদায়িক অপতথ্য প্রচারের ভয়াল রূপ দেখেছে রিউমর স্ক্যানার ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। আমাদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাকে বিস্তৃত পরিসরে দেখাতে এবং ছড়িয়ে দিতে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ফুটেজ যেমন ব্যবহার হয়েছে, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত রূপ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ঘটনাকে৷
অল্প সময়ে এক্সে সাম্প্রদায়িক প্রোপাগান্ডার এমন ব্যাপক প্রচার সাম্প্রতিক বছরগুলোয় লক্ষ্য করা যায়নি৷ অনলাইন ভেরিফিকেশন ও মিডিয়া গবেষণা প্লাটফর্ম ডিসমিসল্যাবের রিসার্চ-লিড মিনহাজ আমানও একই মত দিচ্ছেন। রিউমর স্ক্যানারের সাথে আলাপে তিনি বলেছেন, “২০২১ সালে কুমিল্লাতে মন্দিরের প্রতিমার নিচে কুরআন রাখার সেই ঘটনার পরেও ফেসবুক- টুইটারে বেশ আলোচনা হয়েছিল।” সে সময়ও ভুয়া খবরের প্রচার ঘটেছিল যা বাংলাদেশের ফ্যাক্টচেকাররাই ভুয়া বলে নিশ্চিত করে। মিনহাজ বলছেন, “তবে সেবারের মাত্রাটা বোধ হয় এইবারের মতো এত বেশি ছিল না।”
রিউমর স্ক্যানার মনে করছে, অপতথ্য ছড়ানো এক্স অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য এবার বড় সুযোগ হয়ে এসেছে বাংলাদেশের গত এক মাসের ঘটনাপ্রবাহের অসংখ্য কন্টেন্ট অনলাইনে থাকা। মধ্য জুলাই থেকে আন্দোলন, হামলা, লাশেরসহ বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে অসংখ্য ভিডিও ফুটেজ পোস্ট হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে সহজেই ঘটনাগুলোকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে প্রচার করা হয়েছে৷
ভারতের ফ্যাক্টচেকার অন্কিতা দেশকারের কাছে রিউমর স্ক্যানার জানতে চেয়েছিল, কেন সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক প্রচারের হার বেড়েছে। অন্কিতা বলছেন, “সাম্প্রদায়িক ভুল তথ্য পোস্ট করার মাধ্যমে অ্যাকাউন্টগুলো তাদের ফলোয়ারদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পেয়ে থাকে। অনেকেই তাই নিজেদের এনগেজমেন্ট বা রিটুইট সংখ্যা বাড়াতে এসব অপতথ্য এক্সে শেয়ার করছেন।”
অন্কিতার মতে, এক্ষেত্রে আরেকটি কারণ হতে পারে সামাজিক মাধ্যমে যুক্ত হওয়া ‘বয়স্ক’ ব্যক্তিদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা। তাদের জন্য এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা এবং তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের কন্টেন্টের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় বা রিটুইট করতে পারে। কারণ এটি তাদের সামনে বেদনাদায়ক হিসেবে উপস্থাপিত হয়।
দেশটির আরেক ফ্যাক্টচেকার ইয়ুশা রহমান একই প্রশ্নের উত্তরে রিউমর স্ক্যানারকে বলেছেন, এই অপতথ্যগুলো প্রচার করছে মূলত ধর্মীয় উগ্রবাদীরা। তাদের মাধ্যমে এসব অপপ্রচার বাড়ছে। তারা সাম্প্রদায়িক প্রচারকে মুসলিম বিরোধী আখ্যান প্রচারের উপায় হিসেবে দেখছে।
মিনহাজ আমান মনে করেন, শুধু ভারত না, ইউরোপেও টুইটারে (বর্তমানে এক্স) ভুয়া খবরের পরিমান বেশি যা গত বছর একটি স্টাডিতে উঠে এসেছিল। কারণ হিসেবে মিনহাজের বক্তব্য, “টুইটার (এক্স) এর কন্টেন্ট মডারেশনের দুর্বলতাগুলো এজন্যে দায়ী। এছাড়া টুইটারের ফ্যাক্টচেকিং পলিসি এবং ফ্লাগিং প্রসেস এখনো যথেষ্ট ক্রিয়াশীল না হওয়ায় যেনতেনভাবে প্লাটফর্মটির অপব্যবহার করছে ইউজাররা। যার সর্বশেষ উদাহরণ ভারত-বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অপতথ্যের বন্যা।”